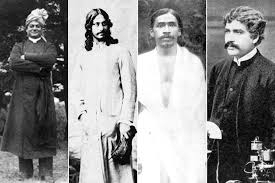∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
বাংলার পট : ঐতিহ্য ও বহুমাত্রিকতা

তরুণ কুমার কর্মকার
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
Doinik Sabder Methopath
Vol-175. Dt -29.10.2020
১২ কার্তিক,১৪২৭. বৃহস্পতিবার
================================
ভারতবর্ষে চিত্রকলার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। সৃষ্টির একেবারে প্রথম দিকে গুহাবাসী মানুষ দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য ছবি এঁকে যে-কলার সৃষ্টি করেছিল তারই রেশ পরম্পরা বাহিত হয়ে আজকের মানুষের হাতে হয়েছে আরো সমৃদ্ধ ও শিল্পিত। এই পরম্পরার মধ্যে ঘটে গেছে অনেক বদল, পালাবদলের ইতিহাসে অনেক ছাপ রয়ে গেছে তার রেখায়। কিন্তু এই চলমানতার মধ্যেও মূলসুর পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি আর সেখানেই থেকে গেছে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। শিল্পকলার মূলত দুই রূপ, নাগরিক বা রাজন্যবর্গের দ্বারা পরিচালিত শিল্পকলা আর লৌকিক বা জনসাধারণের মধ্যে প্রবহমান শিল্পকলা। অজন্তা, ইলোরা, সাঁচি, অমরাবতী বা বিভিন্ন মঠ চৈত্যগুলোতে সেই সমস্ত অভিজাত বা বণিক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্র গড়ে উঠেছে, যেখানে পণ্য পরিবহনের ফাঁকে আশ্রয় নেওয়া যাত্রীদের ক্লান্তি ও ভার লাঘব হতো। কেননা ‘এইসব গুহাগুলি দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত পণ্য ও বাণিজ্য চলাচল প্রসূত অন্তর্দেশীয় শুল্ক আদায়ের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হত। উপরন্তু পণ্যবাহী দলগুলি যাতে এই সব গুহার আশ্রয়ে বিশ্রাম করার এবং সেই সঙ্গে ধর্মশিক্ষা ও সাধনার সুযোগ পায়।’
অপরদিকে লৌকিক চিত্রগুলিতে থাকত বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনির ঘরোয়া আমেজ, যা গ্রামে গ্রামে পরিবেশিত হয়ে আপামর জনসাধারণকে সাহিত্যরসে উদ্বুদ্ধ করত। ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই যে এই লৌকিক চিত্রকলার প্রচলন ছিল তার নিদর্শন হলো পটচিত্রগুলো। ওড়িশার বাসুদেবপুর, রঘুরাজপুর, বিহারের জিতবারপুর, ঝাড়খ–র দুমকা বা পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় পটের প্রচলন দেখা যায়। এমনকি ভারতের বাইরে মিশর, ইসরায়েল, চিন, জাপান, তিববত, নেপাল প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় পটের প্রচলন লোকসাহিত্যের সেই নৃতাত্ত্বিক দিকটিকে তুলে ধরে, যেখানে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব যে একই সংস্কৃতি থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে তাকালে পটের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, বৌদ্ধ সংযুক্তনিকায়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাণভট্টের হর্ষচরিত, বিশাখা দত্তের মুদ্রারাক্ষস, ভাসের প্রতিমানাটক থেকে শুরু করে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র, ভবভূতির উত্তররামচরিত সে-সাক্ষ্যই বহন করে চলেছে। এমনকি বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলোতে বা চৈতন্য আমলেও পটের যে সুখ্যাতি ছিল তা রূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব থেকে জানা যায়।
বাংলার পটগুলো নিছক ছবির ভা-ার নয়। অন্যান্য জায়গার পটের সঙ্গে বাংলার পটের মৌলিক পার্থক্য হলো, এই পটগুলো গান গেয়ে পরিবেশিত হতো। তবে আকার, উপকরণ ও ছবির দিক থেকে অন্যান্য পটের সঙ্গে কিছুটা সৌসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। আকৃতিগত দিক থেকে পট মূলত দুই প্রকার। এক. জড়ানো পট বা দীঘল পট, যেখানে আড়াআড়িভাবে কখনো বা লম্বালম্বিভাবে ছবি আঁকা থাকে। দুই. চৌকো পট বা একটি ছবি নিয়ে আঁকা পট। কালীঘাটের পট চৌকো পট হিসেবে পরিচিত, যদিও চৌকো পট আয়তাকার, বর্গাকার বা গোলাকার হয়ে থাকে। জড়ানো পট বা দীঘল পটের সঙ্গে গান যুক্ত থাকে। পটুয়ারা গান গেয়ে পটের কাহিনি বলে যান। এই জড়ানো পট উচ্চাঙ্গের বা উৎকৃষ্ট মানের রসযুক্ত। বিষয়গত দিক থেকে পটকে পৌরাণিক লীলা কাহিনিমূলক, পাঁচ কল্যাণী বা পাঁচ মিশালি কাহিনির সংমিশ্রণ নিয়ে রচিত পট ও গোপালন বিষয়ক – এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। পরবর্তীকালে আরো বিষয় সংযোজিত হয়। তবে কালীঘাটের পটের বিষয় বিচিত্র। জেলাভিত্তিক পটের বিষয় আলাদা হয়ে থাকে, যেমন মেদিনীপুর জেলার পটের বিষয় বিভিন্ন। রামায়ণ থেকে সিন্ধুবধ, রামের বনবাস, সীতাহরণ, সেতুবন্ধন, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, রাবণবধ ইত্যাদি মহাভারত থেকে দাতাকর্ণ, হরিশচন্দ্রের কাহিনি, সাবিত্রী সত্যবানের কথা, ভাগবত থেকে কৃষ্ণের জন্মকথা, ননি চুরি, কালীয়দমন, নেŠকাবিহার, বস্ত্রহরণ ইত্যাদি পুরাণ থেকে শিব-পার্বতীর কথা, সতীর দেহত্যাগ, অসুর বধ, শিবের শাঁখা পরানো, মঙ্গলকাব্য থেকে মনসার কথা, বেহুলা লখিন্দরের কথা, কমলেকামিনীর কথা, শ্রীমন্ত সদাগরের কথা, তাছাড়া চৈতন্য কথা, সত্য নারায়ণের কথা, জগন্নাথের কাহিনি ও যমপট ইত্যাদি।
বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর এলাকায় বিষ্ণুপুরি পট ও বেলিয়াতোড় এলাকায় বেলেতোড়ি পট পাওয়া যায়, যার বিষয় হলো যম পট, জগন্নাথ পট। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সিঞ্চবোঙা, মারাংবুরু পট, দুর্গাপট, লক্ষ্মীপট, দশাবতার পট দেখানো হতো। মুর্শিদাবাদের পটের বিষয় একই, তবে ঘরানার ছাপ আছে, নকশার কাজেও স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। পুরুলিয়ার আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে চক্ষুদান পট খুবই উলেস্নখযোগ্য। এই পটে দেখা যায় পটুয়ারা মৃত ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে এই পট দেখাতেন, পটে ব্যক্তির চোখ আঁকা থাকত না ফলে তাঁরা বলতেন, চোখের অভাবে ব্যক্তিটি মৃত্যুলোকে খুবই কষ্ট পাচ্ছে তাই উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে তাঁরা চক্ষুদান করে ব্যক্তির আত্মার শান্তির ব্যবস্থা করতেন। বীরভূমের পটে যমপট বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পটে বিভিন্ন বিষয়ের শেষে যমপট থাকবেই যার বিষয় হলো মৃত্যু-পরবর্তী কর্মফল ভোগ। এছাড়া অন্যান্য জেলায় রামলীলা বা কৃষ্ণকথা, বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি, শিব মাহাত্ম্য, চৈতন্যলীলা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পটগুলো অঙ্কিত হয়েছে। অপরদিকে চৌকো পটে গান থাকে না আর বিষয়েও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়, যেমন দুর্গা, কালী, গণেশ, লক্ষ্মী, শিব প্রভৃতি দেব-দেবী থেকে শুরু করে পশুপাখি, সবুজ রঙের বাঘ, মাছের ছবি, এমনকি উনিশ শতকের ইংরেজ আমলের নববাবু সমাজ ও তাদের ভ্রষ্টতা, পানাহার, বারবণিতা গমন ইত্যাদি নানা সামাজিক বিষয় নিয়ে এই চৌকো পট আঁকা হয়েছে।
উপকরণের দিক থেকে পটগুলো প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে।
পট মূলত কাপড়ের ওপর আঁকা ছবি আর লোকসাহিত্য হিসেবে উপকরণগুলো শিল্পীকেই সংগ্রহ করে নিতে হয়, তাই বিভিন্ন দেশজ সহজলভ্য উপাদানকেই তাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের শিল্পে। কাপড় রং করার জন্য দেশি নীল, এলামাটি, খড়িমাটি, গেরিমাটি, সিন্দুর, হলুদ, ভুসা কালি, প্রদীপের কালি, গাছের পাতা, শিম বীজ, হিঞ্চে শাক, পাকা তেলাকুচা ইত্যাদির ব্যবহার হতো আর বেলের আঠা, তেঁতুলের বীজকে আঠা হিসেবে লাগানো হতো। পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিমের আঠা দেওয়া হতো। রং গোলার জন্য ব্যবহৃত হতো নারকেলের মালা। তুলি হিসেবে কাঠবেড়ালির লোম, ছাগলের লোম, বেজির চুল ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে কাপড়ের বদলে কাগজের পট এবং রঙের ক্ষেত্রে ফেব্রিক বা কেমিক্যাল রং ব্যবহৃত হয়।
পটুয়া সংগীতগুলোর মূল্য অপরিসীম। ছবির সঙ্গে যে-গান গাওয়া হতো তাতে ফুটে উঠত বাঙালি হৃদয়ের সুর। কাহিনিগুলোর যে যে অংশ বাঙালি মনের সঙ্গে মিল আছে সেই অংশগুলোকে নির্বাচন করে দরদভরা গলায় তা দর্শকের কাছে পরিবেশন করা হতো। তাই অধিকাংশ কাহিনিই হয়ে উঠেছে বাঙালির নিজস্ব কাহিনি। কাশীরাম দাসের মহাভারত বা কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেমন বাঙালির ঘরের কথাকে কাব্যে তুলে ধরেছে, তেমন এই সমস্ত পটুয়া সংগীতগুলো কোন প্রাচীনকাল থেকে লোকমুখে প্রচারিত হয়ে সুখ-দুঃখের কথাকে আপন করে নিয়ে কথকতায় ভরা গ্রামবাংলার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। সেজন্যই পটুয়া গানের সংগ্রাহক গুরুসদয় দত্ত তাঁর পটুয়া সঙ্গীত গ্রন্থে বলেছেন, ‘ধর্ম্ম, দর্শন ও পুরাণের মূল তত্ত্বগুলি যে বাঙালি হিন্দু সমাজের গণ-জীবনে অতি সহজভাবে অনুসঞ্চারিত হইয়া দৈনন্দিন ভাব ও চিন্তাধারার অঙ্গীভূত হইয়াছিল তাহার একটি বিশেষ পরিচয় আমরা এই পটুয়া সঙ্গীতের মধ্যে পাই।’২ তাই দেখা যায়, পটের দেব-দেবীরা বাঙালি গৃহস্থের মতো আচরণ করে। কৃষ্ণের অবতার পটে রাধা কৃষ্ণকে অনুরোধ করে বলে –
গাছ হতে নাম ঠাকুর পেড়ে দাও ফুল
ডাল ভেঙ্গে প’ড়ে মরবে শূন্য হইবে কুল।
রাধার কেশ পরিচর্যার বর্ণনায় ভেসে ওঠে গৃহস্থ বাঙালি বধূর ছবি –
কেশ গুলি আঁচুড়িয়ে করেন গোটা গোটা
কেশের মাঝে তুলে দিছে সিন্দুরের ফোঁটা।
পটুয়ারা ছবির সঙ্গে সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোকে গানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতেন। মূল ঘটনাটি ছবিতে আঁকা থাকত কিন্তু কাহিনির যত অগ্রগতি ঘটত তার সঙ্গে তাল মেলাবার জন্য ছবিতে যেগুলো উলেস্নখ নেই তা তারা বিশ্লেষণ করে দিতেন, যা অনেকটা নাটকের সংলাপের মতো হতো। ‘রামণ্ডলক্ষ্মণ’ পটে সেরকম একটি বর্ণনা রয়েছে –
(আজ) সূপর্ণখা নয়ন বাঁকা আড় নয়নে চায়
(আজ) বিয়ে কর বিয়ে কর বলে লক্ষ্মণের কাছে যায়।
লক্ষ্মণ বলে আমি চৌদ্দ বছর খেদা রাখবো না কি নিদ্রা যাব না
পোড়ামুখী আমার সম্মুখ থেকে বিদায় হ।
ওই কথা শুনে সেদিন একটা দুবর্ববাক্য বলিল
ক্রোধ করে, বিমুখ হয়ে রাবণের ভগ্নীর সেদিন নাসিকা কাটিল।
‘সিন্ধু বধ’ পটে বাঙালি মাতৃহৃদয়ের ছবি ফুটে উঠেছে, ‘কে এলি বাপ সিন্ধুক এলি বলরে বচন/ মা বলিয়া ডাকরে বাপ জুড়াক রে জীবন।’
দাম্পত্যজীবনের ছবি পাওয়া যায় ‘শঙ্খ পরান পালা’গুলোতে।
শিব-পার্বতীর সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্য ও তার মাঝে রসিকতাপূর্ণ বাক্যালাপ যেন সকল বাঙালি কবির কাছে আলোচ্য ও উপভোগ্য বিষয়। গৌরীর শাঁখা পরবার সাধ হয়েছে তাই স্বামীকে আবদার করে ‘আঙ্গা উলি’ অর্থাৎ রাঙা রুলি কিনে দেওয়ার জন্য; কিন্তু শিব জানে তার সংসারের হাল, তাই গৌরীকে জ্ঞানের কথা শোনায় –
রূপাসোনা পর গৌরী আকালে বিচে খাবি
আঙ্গা উলি শঙ্খ পরে কোন সরগে যাবি।
স্বামীর মুখ থেকে এ-কথা শোনামাত্র গৌরী আর ঠিক থাকতে পারেনি। নারী অভিমানে ঘা পড়তেই সে মুখরা হয়ে উঠেছে আর এতই উগ্র হয়েছে যে তার রেশ মা-বাপ পর্যন্ত গিয়ে থেমেছে –
মর মর ভাঙ্গর বুড়ো চক্ষক্ষ পড়ুক ছানি
চোকে না দেখতে পাবি হীরে লাল কুচুনী।
চোখ খাক তোর মাতা পিতা চোক খাগা তোর খুড়ো
জেনেশুনে বিয়ে দিলে লাঠি ধরা বুড়ো।
একথা বলেই গৌরী ছেলেপিলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাপের বাড়ির উদ্দেশে। বাধ্য হয়ে শিবকেও যেতে হয় এবং শাঁখা পরিয়ে তবে নিস্তার পাওয়া যায়। কিন্তু এইভাবে সংসার চলে না, তাই বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য গৃহিণী পরামর্শ দেয় ভিক্ষা ছেড়ে চাষাবাদ করতে। নিত্যদিনের চালের ব্যবস্থা করা সাধারণ মানুষের কাছে খুবই কষ্টকর। আর সেই জীবনসংগ্রামের ছবি যেন পটের মাধ্যমে কিছুটা উপস্থাপিত হয়েছে। তাই ‘চাষপালা’তে উত্তম গৃহিণীর মতো গৌরী বলে –
ভুঁই এ লাগাও মুগ-মুশুরী পগারে লাগাও কলা
নৈবেদ্য বাড়বে ঠাকুর ধর্ম্ম সেবার বেলা।
অবশেষে শিব চাষ করে উত্তম ধান ফলায়; কিন্তু বাড়ি ফিরতে চায় না। কেননা তার নতুন বাতিক এখন মাছ ধরায়, তাই দুর্গাকেও যেতে হয় বাগদিনী সেজে মাছ ধরতে। ‘শিবের মাছ ধরা’ পটে সেই দৃশ্য ফুটে উঠেছে। অপরদিকে গোপালন পটে গরুর উপকারিতা বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গরু-সেবার জন্য কেবল বাড়ির বউদেরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই নীলবতী সাতদিনে সাত বউকে বলেছে –
সাত বউকে ডাক দিয়ে কহে নীলবতী
গরু বাছুর সেবা কর তোমরা নিত্যি নিত্যি।
নারীদের এই পরিশ্রমের মধ্যে তাদের বেদনার কথাও গানের মধ্যে পাওয়া যায় –
বউ বলে নিগরুর ঘরে যদি মোর বিবাহ হইত
তবে কেন সোনার শঙ্খয় গোবর লাগিত।
পরবর্তীকালে পটগুলোতে বিভিন্ন বিষয় যোগ হতে থাকে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পটের বিষয়বস্ত্তও পালটাতে শুরু করে। জীবিকার তাগিদে পটুয়াদের বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়কে কখনো স্বেচ্ছায়, কখনো বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয়। তাই পৌরাণিক পটের পাশাপাশি ঐতিহাসিক, সমাজ সচেতনতামূলক, জীবনীমূলক, ধর্মগুরু বিষয়ক, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ্যমূলক, পরিবেশ সচেতনতামূলক, রাজনৈতিক প্রচারবিষয়ক পটের প্রচলন হয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ, অসহযোগ আন্দোলন, নেতাজি, গান্ধীজি, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, মাতঙ্গিনী, পণপ্রথা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, কুসংস্কার, সাক্ষরতা, পালস পোলিও টীকাকরণ, শিশুকল্যাণ, কুষ্ঠ, এইডস, বৃক্ষরোপণ, ভোটযুদ্ধ, কালোবাজারি, সুন্দরবন, গাজীপীরদের মাহাত্ম্য, ট্যাক্স প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে গান রচিত হতে থাকে। তবে এসব গানের সুর পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে রচিত পটের সুরের থেকে আলাদা। সচেতনতামূলক গানগুলোর সুর যেন ঘোষকের মতো। কোথাও কবিগানের চটুলতা, কোনো গানে বাউলের সুর, চারণকবিদের মতো উদাত্ত সুর, ফকির-দরবেশের সুর, আবার কীর্তনগানের মতো ভক্তিরসের আমেজও পাওয়া যায়। পটুয়ারা যেহেতু না-হিন্দু না-মুসলিম, তাই তাঁদের গানে মিশ্র সংস্কৃতির সহাবস্থান লক্ষ করার মতো। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে হিন্দু-মুসলমানদের নিয়ে
যে বিভেদ দেখা যায় তা তাঁরা মেনে নিতে পারেন না, তাই প্রশ্ন তোলেন –
ভারতবর্ষ সবার দেশ, সবার সে যে ঘর।
হিন্দু মুসলিম সব জাতি কেহ নাই পর \
মন্দির মসজিদ নিয়ে আজ প্রশণ কেন দেশে।
হিংসা কেন দাঁড়াল আজি সবার দ্বারে এসে \
বাংলার পটের এসব বিভিন্ন দিক সংযোজিত হতে থাকে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতক থেকে। ইংরেজদের আগমন, জমিদারি ব্যবস্থার অত্যাচার ও মিথ্যা জৌলুস, বাবুসমাজের নীতিহীনতা, নাগরিক বৈভবের কলুষতা ইত্যাদি বিষয় সাহিত্য-গানে-ছবিতে প্রতিফলিত হতে থাকে। কালীঘাটের পটচিত্রে তাই দেখা যায় ছবিগুলোর ভিন্নমাত্রা। রাজা সাধন চৌধুরী কর্তৃক বর্তমান কালীঘাট মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর জনসমাগম ও সেই উপলক্ষ্যে জীবিকার জন্য পটুয়ারা পট আঁকতে শুরু করেন, যা একসময় বিভিন্ন জেলাতেও রপ্তানি হতে শুরু করে। এসব পটে দেব-দেবীর ছবির পাশাপাশি ব্যঙ্গাত্মক সমাজচিত্র ছিল লক্ষ করার মতো। দেব-দেবীর সাজসজ্জা ছিল সাহেব-মেমদের মতো। এছাড়া নারী জাতির অবমাননা, বাইজিবিলাস, ভ্রষ্টাচারী গুরু ইত্যাদি বিষয়ও অঙ্কিত হতো। সামাজিক বিষয়কে প্রতীকের মাধ্যমে দেখানো হতো এই পটে, যেমন বিড়ালের মুখে চিংড়ি মাছের মোটিফ বা সিংহের মুখে মানুষ, বিড়ালের বিবাহ, বুলবুলির লড়াই ইত্যাদি। কালীঘাটের পটে রঙের ব্যবহার ও অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল আকর্ষণীয়। এ-ব্যাপারে অশোককুমার রায় ‘কালীঘাটের পটচিহ্ন’ প্রবন্ধে বলেছেন, ‘ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কিছু অবয়বধর্মী কালীঘাট পট সংগ্রহ আছে যাতে ভারতীয় শৃঙ্গার, সোভারী, দেহসৌষ্ঠব দর্শককে যুগপৎ বিস্মিত ও মুগ্ধ করে।’
ফলে কালীঘাটের পট একটি ভিন্নমাত্রা যোগ করে।
বাংলার এই লোকায়ত সংস্কৃতি আপামর জনসাধারণের শুধু মনোরঞ্জনই করেনি, পাশাপাশি বিভিন্ন দিককেও তুলে ধরেছে। একদিকে যেমন এই শিল্প লোকশিক্ষার সহায়ক হয়েছে, তেমন তাতে ধরা পড়েছে পৌরাণিক কাহিনির বাঙালি রূপ, নারীর অবহেলিত জীবন, পুরুষতান্ত্রিকতা, মনস্তত্ত্ব, নৈতিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি, আবার তার সঙ্গে সাধারণ দর্শক-শ্রোতা পেয়েছে ছবি দেখার সুযোগ, গল্প শোনার আমেজ, নাটকের আনন্দ ও সুরের আবেশ। তবে বাঙালির এই ঐতিহ্য যুগের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকে। ভিন্ন সাংস্কৃতিক আবহে ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে এই পরম্পরা। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সামাজিক অবস্থানের জন্য পটুয়ারা
পেশা বদল করতে শুরু করেছেন। অর্কেস্ট্রা, ডিজে ও প্রমোদমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে তাদের ভিন্ন পথ বেছে নিতে হচ্ছে। ডেবরার বাঘাবেরিয়া গ্রামের ফুলজান চিত্র কর জানাচ্ছেন, ‘একসময় রাত জেগে পটের গান গাওয়া হতো; কিন্তু এখন ছেলেমেয়েরা কলেজে পড়াশোনা করছে, তাই তারা পট নিয়ে গ্রামে ঘুরে গান শোনাতে অনিচ্ছুক।’ তবে সরকারি কোনো অনুষ্ঠানে বা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে ডাক আসে বলে তিনি জানিয়েছেন। অনেক জায়গায় সরকারি ভাতাও দেওয়া হয়ে থাকে প্রতিমাসে। কিন্তু ক্রমেই নষ্ট হতে চলেছে এই সংস্কৃতি। অবশ্য অনেক পটশিল্পকে বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে ক্রাফটের মাধ্যমে তাদের শিল্পকলা ফুটিয়ে তুলে বাণিজ্যের কাজে লাগানো হচ্ছে, ফলে জীবিকা অর্জনের পথ কিছুটা হলেও সুগম হচ্ছে। তবে এ-ব্যাপারে সরকারকেই আরো এগিয়ে আসতে হবে। পেইন্টিং বা ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে শিল্পীদের সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে প্রচার ও প্রসার ঘটিয়ে পটশিল্পকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে হবে, তাহলে হয়তো যোগ হতে পারে আরো একটি মাত্রা। আর তখনই বিশ্বকবির ভাষায় সকলে বলে উঠতে পারব –
এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆