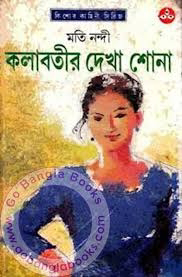Sunday, 11 July 2021
জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য। আল মাহমুদ ও ঝুম্পা লাহিড়ী। ১১.০৭.২০২১. Vol -430. The blogger in literature e-magazine
Saturday, 10 July 2021
জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য। মতি নন্দী। ১০.০৭.২০২১. VOL - 429. The blogger in literature e-magazine.
মতি নন্দী
১০ জুলাই ১৯৩১ সালে উত্তর কলকাতায় তারক চ্যাটার্জি লেনে জন্ম . পিতা চুনিলাল নন্দী ও মাতা নলিনীবালা নন্দী .মতি নন্দীর মা ছিলেন তার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। চার ভাই ও এক বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তার পূর্বপুরুষদের পদবী দে সরকার। পিতামহ তার চাকুরী সূত্রে বদল করে নন্দী গ্রহণ করেন। মতি নন্দীর পিতা সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। বাল্যকালেই তিনি পিতৃহারা হয়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে গল্প লেখার মধ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা হয়। ১৯৫৬ তে দেশ পত্রিকায় ছাদ গল্প এবং পরিচয় পত্রিকায় চোরা ঢেউ প্রকাশিত হয়।১৯৪৮ সালে স্কটিশচার্চ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকপাস করে ১৯৫০ সালে I.S.C পাস করেন এবং ১৯৫১ সালে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং করেন।আবার ১৯৫৭ সালে মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে বাংলা সাহিত্যে অনার্স সহ গ্রাজুয়েশন পাস করেন। ক্রীড়া সাংবাদিক হিসাবে আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করতেন। লস অ্যাঞ্জেলেস ও মস্কো অলিম্পিক, দিল্লি এশিয়ান গেমস কভার করেছেন তিনি। ক্রীড়ামূলক সাহিত্য রচনার পাশাপাশি বলিষ্ট উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখেছেন তিনি। তিনি আনন্দ পুরষ্কা্রে সম্মানিত হন। দীর্ঘদিন আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন। কোনি, স্টপার, স্ট্রাইকার উপন্যাস বা কলাবতী সিরিজের পাশাপাশি সাদা খাম, গোলাপ বাগান, উভয়ত সম্পূর্ণ, আর বিজলীবালার মুক্তি ইত্যাদি উপন্যাস রচনা করেছেন মতি নন্দী।
উপন্যাস
- সাদা খাম (আনন্দ পাবলিকেশন)
- উভয়ত সম্পূর্ণ (আনন্দ পাবলিকেশন)
- গোলাপ বাগান (আনন্দ পাবলিকেশন)
- ছায়া (আনন্দ পাবলিকেশন)
- ছায়া সরণীতে রোহিণী (আনন্দ পাবলিকেশন)
- জীবন্ত (আনন্দ পাবলিকেশন)
- দুটি তিনটি ঘর (আনন্দ পাবলিকেশন)
- দ্বিতীয় ইনিংসের পর (আনন্দ পাবলিকেশন)
- দূরদৃষ্টি (আনন্দ পাবলিকেশন)
- পুবের জানালা (আনন্দ পাবলিকেশন)
- বনানীদের বাড়ি (আনন্দ পাবলিকেশন)
- বিজলীবালার মুক্তি (আনন্দ পাবলিকেশন)
- মালবিকা (আনন্দ পাবলিকেশন)
- শিবি (আনন্দ পাবলিকেশন)
- শোলোকে পনেরো করা (আনন্দ পাবলিকেশন)
- সহদেবের তাজমহল (আনন্দ পাবলিকেশন)
- সবাই যাচ্ছে (আনন্দ পাবলিকেশন)
- দশটি উপন্যাস (আনন্দ পাবলিকেশন)
- "নক্ষত্রের রাত (পুনশ্চ)
- বাওবাব (পুনশ্চ)
- দাদাশ বাকতি (পুনশ্চ)
- নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান (পুনশ্চ)
- "বারান্দা"
- "করুণাবাস্ততা"
- "ছোটবাবু"
ছোটদের
- কোনি(আনন্দ পাবলিকেশন)
- অলৌকিক দিলু(আনন্দ পাবলিকেশন)
- স্টপার(আনন্দ পাবলিকেশন)
- স্ট্রাইকার(আনন্দ পাবলিকেশন)
- কুড়ন(আনন্দ পাবলিকেশন)
- জীবন অনন্ত(আনন্দ পাবলিকেশন)
- নারান(আনন্দ পাবলিকেশন)
- ফেরারি(আনন্দ পাবলিকেশন)
- তুলসী(আনন্দ পাবলিকেশন)
- দলবদলের আগে(আনন্দ পাবলিকেশন)
- মিনু চিনুর ট্রফি(আনন্দ পাবলিকেশন)
- এমপিয়ারিং
- ধানকুড়ির কিংকং(আনন্দ পাবলিকেশন)
- বিশ্ব-জোড়া বিশ্বকাপ(আনন্দ পাবলিকেশন)
- বুড়ো ঘোড়া(আনন্দ পাবলিকেশন)
- দৃষ্টি কিশোর উপন্যাস(আনন্দ পাবলিকেশন)
- ক্রিকেটের আইন কানুন(আনন্দ পাবলিকেশন)
- ভুলি(গাঙচিল)
- শিবা(আনন্দ পাবলিকেশন)
দশটি কিশোর উপন্যাস
- ননিদা নট আউট
- স্ট্রাইকার
- স্টপার
- অপরাজিত আনন্দ
- দলবদলের আগে
- ফেরারি
- আম্পায়ারিং
- তুলসী
- নারান
- মিনু চিনুর ট্রফি
কলাবতী সিরিজ
- কলাবতী
- কলাবতীদের ডায়েট চার্ট
- কলাবতীর দেখা শোনা
- কলাবতী ও খয়েরি
- ভূতের বাসায় কলাবতী
- কলাবতী, অপুর মা ও পাঁচু
- কলাবতী ও মিলেনিয়াম ম্যাচ
- কলাবতীর শক্তিশেল
সিনেমা
১৯৭৮ সালে তার উপন্যাস অবলম্বনে অর্চন চক্রবর্তীর পরিচালনায় স্ট্রাইকার চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়। এই ছবিতে মূল চরিত্রে অভিনয় করেন সমিত ভঞ্জ। ১৯৮৬ সালে সরোজ দে পরিচালিত এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত 'কোনি' চলচ্চিত্রটি মতি নন্দীর একই নামের বাংলা উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত। এছাড়াও তার "জলের ঘূর্ণি ও বকবক শব্দ" গল্প অবলম্বনে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতা অনিমেষ আইচ ২০১৭ সালে ভয়ংকর সুন্দর ছবিটি নির্মাণ করেন। পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং আশনা হাবিব ভাবনা এ ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন।
পুরস্কার ও সম্মাননা
Friday, 9 July 2021
আলোচনা পর্ব। শিশু-কিশোর মনের কাল্পনিক চরিত্র। ০৯.০৭.২০২১. Vol -428 The blogger in literature e-magazine
Ans: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রশ্নঃ ‘জয়গুন’ কোন উপন্যাসের চরিত্র?
Ans: সূর্যদীঘল বাড়ি
প্রশ্নঃ ‘গয়া’ কোন গল্পের চরিত্র?
Ans: মামলার ফল
প্রশ্নঃ ‘রতন’ চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কোন ছোট গল্পের?
Ans: পোস্টমাস্টার
প্রশ্নঃ ‘মুর্দা ফকির’ চরিত্রটি কোন নাটকের?
Ans: কবর
প্রশ্নঃ ‘তিলোত্তমা’ চরিত্রটির স্রষ্টা ঔপন্যাসিক-
Ans: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রশ্নঃ ‘আদুরী’ চরিত্রটি কোন নাটকের?
Ans: নীলদর্পণ
প্রশ্নঃ ‘অপর্ণা’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে নাটকের চরিত্র–
Ans: বিসর্জন
প্রশ্নঃ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের বড়ায়ি কি ধরনের চরিত্র?
Ans: রাধাকৃষ্ণে প্রেমের দূতী
প্রশ্নঃ ‘রোহিনী’ কোন উপন্যাসের নায়িকা?
Ans: কৃষ্ণকান্তের উইল
প্রশ্নঃ রোহিণী-বিনোদিনী-কিরণময়ী কোন গ্রন্থগুচ্ছের চরিত্র ?
Ans: কৃষ্ণকান্তের উইল-চোখের বালি-চরিত্রহীন
প্রশ্নঃ ‘ঠকচাচা’ চরিত্রটি কোন উপন্যাসের?
Ans: আলালের ঘরের দুলাল
প্রশ্নঃ নদের চাঁদ কোন পালাগানের চরিত্র?
Ans: মহুয়া
প্রশ্নঃ ‘অর্জুন’ চরিত্রটি কোন গ্রন্থের?
Ans: চিত্রাঙ্গদা
প্রশ্নঃ ‘গৃহদাহ’ উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম কি?
Ans: সুরেশ ও অচলা
প্রশ্নঃ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র কে?
Ans: ইন্দ্রনাথ
প্রশ্নঃ মনসামঙ্গলের চরিত্র কোনটি?
Ans: সনকা
প্রশ্নঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মহেশ গল্পের প্রধান চরিত্র কে?
Ans: গফুর
প্রশ্নঃ বিদ্রোহী বালিকা বধূ ‘জামিলা’ কোন উপন্যাসের চরিত্র?
Ans: লালসালু
প্রশ্নঃ জাগো বাহে কুণ্ঠে সবাই’- এই অবিস্মরণীয় আহ্বানউচ্চারণরণ করে কোন চরিত্রটি?
Ans: সৈয়দ শামসুল হকের ‘নূরুল দীনের সারাজীবন’ নাটকের নূরুল দীন
প্রশ্নঃ ‘হেমাঙ্গিনী’ ও ‘কাদম্বিনী’ কোন বিখ্যাত গল্পের দুই চরিত্র?
Ans: মেজদিদি
প্রশ্নঃ ‘অর্পণা’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকের নায়িকা?
Ans: বিসর্জন
প্রশ্নঃ ‘রাজলক্ষ্মী’ চরিত্রের স্রষ্টা ঔপন্যাসিক-
Ans: শরৎচন্দ্র
প্রশ্নঃ বড়াই ও ধারা চরিত্রদ্বয়ের স্রষ্টা কে?
Ans: চণ্ডীদাস
প্রশ্নঃ ভাডুদত্ত কোন কাব্যের চরিত্র?
Ans: চণ্ডীমঙ্গল
প্রশ্নঃ ‘অভয়া’ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাসের চরিত্র?
Ans: শ্রীকান্ত
প্রশ্নঃ ধনপতি সওদাগর কোন নগরের অধিবাসী ছিলেন?
Ans: উজানীনগর
প্রশ্নঃ কোন চরিত্রটি ‘লালসালু’ উপন্যাসে নেই?
Ans: করিমা বিবি
প্রশ্নঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম-
Ans: গোবিন্দলাল ও রোহিনী
প্রশ্নঃ ভিখু, পাঁচী কোন গল্পের চরিত্র?
Ans: প্রাগৈতিহাসিক
প্রশ্নঃ ‘রহমত’ চরিত্র কোন গল্পের?
Ans: কাবুলিওয়ালা
প্রশ্নঃ ‘আলালের ঘরের দুলাল’ উপন্যাসের চরিত্র কোনটি?
Ans: তিনটিই
প্রশ্নঃ ‘কপাল কুণ্ডলা’ উপন্যাসের নায়কের নাম কি?
Ans: নবকুমার
প্রশ্নঃ শশী, কুসুম চরিত্র দুটির স্রষ্টা কে?
Ans: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রশ্নঃ ‘অন্নদা দিদি’ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাসের চরিত্র?
Ans: শ্রীকান্ত
প্রশ্নঃ ‘নিমচাঁদ’ চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?
Ans: সধবার একাদশী
প্রশ্নঃ শকুন্তলা চরিত্রটির স্রষ্টা কে?
Ans: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
প্রশ্নঃ ‘চাঁদ সওদাগর’ বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র?
Ans: মনসামঙ্গল
প্রশ্নঃ ‘রাজলক্ষ্ণী’ চরিত্রের স্রষ্টা কোন ঔপন্যাসিক?
Ans: শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রশ্নঃ ‘মৃন্ময়’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ছোট গল্পের নায়িকা?
Ans: সমাপ্তি
প্রশ্নঃ শর্মিলা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কোন উপন্যাসের নায়িকা?
Ans: দুইবোন
প্রশ্নঃ রবীন্দ্রনাথের ‘ছুটি’ গল্পের চরিত্র কোনটি?
Ans: ফটিক
প্রশ্নঃ অমিত ও লাবণ্য কোন উপন্যাসের চরিত্র?
Ans: শেষের কবিতা
প্রশ্নঃ ‘রোহিণী’ চরিত্রটি কোন উপন্যাসের?
Ans: কৃষ্ণকান্তের উইল
প্রশ্নঃ নিচের কোনটি শরৎ সাহিত্যের চরিত্র নয়
Ans: সুরবালা
প্রশ্নঃ ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের নায়ক কে?
Ans: অমিত রায়
প্রশ্নঃ বড়াই ও রাধা চরিত্র দুটি কোন গ্রন্থের?
Ans: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
প্রশ্নঃ ধর্মমঙ্গলের চরিত্র কোনটি?
Ans: তিনটিই
প্রশ্নঃ কোনটি ‘লালসালু ’ উপন্যাসের চরিত্র নয়?
Ans: মাজেদা
প্রশ্নঃ ‘কপাল কুণ্ডলা’ কোন প্রকৃতির রচনা?
Ans: রোমান্সমূলক উপন্যাস
প্রশ্নঃ ‘বিষাদ সিন্ধু’ উপন্যাসের নায়কের নাম লিখুন?
Ans: ইমাম হোসেন
প্রশ্নঃ ‘অপু ও দূর্গা’ চরিত্র দুটি কোন উপন্যাসের?
Ans: পথের পাঁচালী
প্রশ্নঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিম্নোক্ত কোন তিনটি গল্পেই মুসলমান চরিত্র রয়েছে?
Ans: ক্ষুধিত পাষাণ, মুকুট ও সুভা
প্রশ্নঃ খুল্লনা ও লহনা চরিত্রদ্বয় কোন কাব্যের অন্তর্গত?
Ans: চণ্ডীমঙ্গল
প্রশ্নঃ ‘ঠক চাচা’ চরিত্রটি কোন উপন্যাসে পাওয়া যায?
Ans: আলালের ঘরের দুলাল।
Thursday, 8 July 2021
আলোচনা পর্ব। শিশু-কিশোর মন গল্প গড়ে। ০৮.০৭.২০২১. VOL -427. The blogger in literature e-magazine
শিশুকে ভাষা শেখানোর অন্যতম সহজ উপায় হলো গল্প বলা এবং সেই গল্প আবার শিশুর কাছ থেকে শোনা। গবেষনায় দেখা যায় শিশু গল্প শোনা ও গল্প বলার মধ্য দিয়ে অনেক নতুন নতুন শব্দ শিখতে ও ব্যবহার করতে পারে। এমনকি অনেক জটিল বাক্যও তারা এই পক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বলতে শিখে। গুছিয়ে কথা বলতে পারে। মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।
গল্প আকারে শিশুরা কোন কিছু সবচেয়ে ভাল মনে রাখতে পারে। যে কারনে শিশুদের শিা নিয়ে কর্মরত অনেক বিশেষজ্ঞই শিশুদের পাঠক্রম তৈরীর ক্ষেত্রে গল্প বলা বিষয়টিকে কিংবা গল্পকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠক্রম সাজানোকে গুরত্ব দিয়ে থাকেন। গল্প বলা বিষয়টিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে এর যে আকর্ষন শক্তি তাতে কোন কিছু মনে রাখা, আমোদিত হওয়া,অনুপাণিত হওয়া,সৃজনশীলতা, শেখা ও জানা অনেক সহজ হয়ে যায়।
ছোট শিশুদের অর জ্ঞান ও ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে উচ্চস্বরে পড়া ও গল্প বলা উভয় পদ্ধতিই খুব কার্যকরী।
কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেন,সরকারী কিংবা বেসরকারী শিশু শিা প্রতিষ্ঠানে এই বিষয়টিকে গুরত্ব দেয়া হয় না। কোথাও কোথাও পাঠক্রমে গল্প বিষয়টিকে রাখা হলেও গল্প বলার পরিবেশ কিংবা গল্প বলার কৌশল জানা না থাকায় বিষয়টি শিশুদের আকৃষ্ট করতে পারে না। শৈশবে বাড়িতে যৌথপরিবারে দাদাদাদী,নানা-নানী কিংবা অন্যকেউ এবং একক পরিবারে মা-বাবা শিশুকে অনেক ধরনের গল্প শোনায় কিন্তু স্কুলের কাশে গল্প বলার ঘটনা সেভাবে ঘটে না। প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে (৩-৫) বছর বয়সী শিশুদের ভাষার দতা অর্জনে এটি খুবই গুরত্বপূর্ন। মনে রাখতে হবে গল্প বলা শিশুদের জন্য শুধুমাত্র বিনোদনের মাধ্যম নয়। শিশুরা গল্প শুনতে ও বলতে ভালবাসে এটা তাদের জন্য আনন্দের। আর আনন্দের বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে কাশ রুমে পড়ার সঙ্গে মিলিয়ে শিশুদের যদি মজার মজার গল্প শোনানো যায় এবং সেই গল্পগুলো পুনরায় তাদের কাছ থেকে শোনা যায় তবে অল্প পরিশ্রমেইছোট শিশুদের অর জ্ঞান ও ভাষা শেখানো যায়।
বইয়ে গল্প পড়া আর গল্প শোনা এই দুইয়ের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। কেউ যখন গল্প বলে তখন সেটি অনেক বেশী অনানুষ্ঠানিক হয়। বইয়ের পৃষ্ঠায় ছাপানো শব্দের মতো সেগুলো নি¯প্রাণ হয় না। বরং গল্প বলিয়ের ভাষা,অঙ্গভঙ্গি, মুখভঙ্গি ও চোখের ভাষা সবমিলিয়ে পুরো গল্পটি যিনি শোনেন তার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠে। তিনি যেন সবকিছু তার চোখের সামনে ঘটতে দেখেন। এ কারনে গল্প বলা শিশুর ভাষা শেখার েেত্র জোরালো ভূমিকা পালন করে। গল্প বলা শিশুর মৌখিক ও লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশের মতা বাড়ায়। তার শব্দের ভান্ডার বাড়ে। তখন সে জটিল বাক্যও তৈরী করতে শিখে।
ভাষার কাজ হলো যোগাযোগ ঘটানো। একজন মানুষ অন্য আরেকজনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে ভাষা ব্যবহার করে। গল্প বলিয়ের ভাষা ব্যবহার ও গল্প দুয়ে মিলে এমন একটি পরিবেশ তৈরী হয় যা শিশু মনকে আন্দোলিত করে। তখন তারা গল্প শোনার পর নিজেরাই সেই গল্পটি বলতে পারে। এভাবে গল্প বলতে গিয়ে দেখা যায় শিশু যে শব্দ ও ভাষা শুনেছে নিজে বলার সময় নিজে থেকে নতুন শব্দ ও বাক্য বিন্যাস করছে। নিজের ভাষায় গল্পটি বলতে গিয়ে ভাষার উপর তাদের দখল তৈরী হয়। গল্প বলা শিশুকে শ্র“তিলিখন ও গল্প লিখতে উৎসাহিত করে।
প্রারম্ভিক শৈশবকালীন বিকাশ নিয়ে যারা কাজ করেন তারা গল্প বলা বিষয়টিকে খুব গুরত্ব দিয়ে থাকেন। ইসিডি শিকগন যখন ছোট ছোট শিশুদের গল্প শোনান তখন গল্পের চরিত্রগুলো এমনভাবে ফুটিয়ে তোলেন যেন তার শ্রোতারা সহজেই বুঝতে পারে। নানা মুখভঙ্গি,অঙ্গভঙ্গি ও ছবি একে তারা গল্পটি এমনভাষায় বলেন যে শিশুরা সহজেই আমোদিত হয়। তারা আগ্রহ নিয়ে শোনে ও নেক সময় প্রশ্ন করে। অর্থাৎ শিশুরা গল্পে পুরোপুরি মিশে যায়। এর মাধ্যমে শিশুদের মাঝে গুছিয়ে কথা বলা ও মনের ভাব প্রকাশ করার সামর্থ্য তৈরী হয়।শিশুদের উপযোগী এবং বারবার বললেও মন ভরে না এমন গল্প শিশুদের বারবার শোনানো যেতে পারে। এ ধরনের গল্প শুনে শিশুরা কান্ত হয় না এবং আগ্রহ হারায় না।
গল্প বলিয়ে শিকের দায়িত্ব হলো শিশুদের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে শোনার দতা বাড়ানো। সে সঙ্গে তাদেরকে অংশ নিতে উৎসাহিত করা। কারন গল্প বলা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহনের মাধ্যমে শিশু দ্রুততার সঙ্গে ভাষা শিখতে পারে।
সঠিক গল্প বাছাই করা সম্ভব হলে গল্পের মাধ্যমে ছোট শিশুকে অনেক কিছুই শেখানো যায়। শিশুর অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে এমন গল্প বাছাই করতে হবে যেখানে কিছু শব্দ বা বাক্যের পুনরাবৃত্তি আছে। এই ধরনের গল্প বলার সময় দেখা যায় পুনরাবৃত্তিমুলক শব্দ বা বাক্য প্রথমবারের পরে যতবার ব্যবহার হচ্ছে শিশুরা নিজ থেকেই সেই শব্দ বা বাক্য বলছে।
গল্প শোনার মাধ্যমে শিশু শব্দ আকারে ভাষা শোনে যা তাকে ভাষা শিখতে আগ্রহী করে তোলে। গল্প শোনা ও গল্প বলার মাধ্যমে তারা গুছিয়ে কথা বলতে কিংবা নিজের ভাষায় একই গল্প শোনাতে পারে। প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ফলে এখন কম্পিউটার ও ইন্টানেটের মাধ্যমে শিশুরা গল্প ছবি আকারে দেখতেও পারে। ছবিও শব্দসহ গল্প কম্পিউটার, টেলিভিশনে দেখা আর একজন গল্প বলিয়ের কাছ থেকে শোনার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। ইন্টারনেট, কম্পিউটার, টেলিভিশন কোনভাবেই শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে গল্পের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে না যা একজন দ গল্প বলিয়ে করতে পারেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শিশুকে গল্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নিতে পারেন। পুরো কাজটি তিনি গল্প বলার মধ্য দিয়ে করেন। যা শিশুর শেখার েেত্র অনেক বেশী শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।
সক্রিয় শ্রোতা হিসেবে শিশুরা যখন শিকের সঙ্গে মিলেমিশে নিজেও গল্প বানাতে শুরু করে তখন শিশুরা নিজের ভাষায় কথা বলা শুরু করে। এভাবে শিশুদের ভাষাজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়। এর পর গল্প বলা শেষে গল্পের আঙ্গিকে যে প্রশ্নগুলো করা হয় শিশুরা স্বতস্ফূর্তভাবে তাতে অংশ নেয়। এ সময়ে সমাজের নানা অংশ থেকে কাশরুমে আগত শিশুরা তাদের নিজেদের মতো করে গল্পের ব্যাখ্যা দেয় এবং গল্পের সঙ্গে নিজের অভিঙ্গতার মিল খুঁজে বের কেরে। এ সময় তারা গল্পটি নিজের মতো করে পুনরায় বলে।
শিক্ষকদের কাছ থেকে শোনা গল্পটি শিশুরা যখন নিজের ভাষায় পুনরায় বর্ণনা করে তখন শব্দ ও বাক্যের ধারনাগুলো অর্জন করে। একটি ভাললাগা র্গপ যখন শিক ও শিশুরা অনেকবার বলে তখন গল্পের বিষয়বস্তু ও ধারনাগুলো তাদের কাছে অনেক বেশী সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বারবার একই গল্প বললে শিশুদের অংশনেয়ার হারও বাড়ে। এ সময় তারা নিজেদের মতো করে গল্পের কাঠামো, চরিত্র ও বর্ননা বদলায়।
গল্প বলা শিশুদের কল্পনা শক্তি বাড়ায়। গল্প শুনতে শুনতে কিংবা বলতে গিয়ে শিশুরা কল্পনার জগৎ তৈরী করে যেখানকার সবকিছুই তারা দেখতে পায়। এভাবে শিশু প্রথমে গল্প শোনে,এরপর গল্প শুনতে শুনতে গল্প বলায় অংশ নেয় এবং সবশেষে শিশু নিজেই গল্প বলিয়ে হয়।
শিশুরা যখন গল্প বলা শুরু করে তখন যে তারা স্কুলেই গল্প বলতে ভালবাসে তা নয়। তারা বাড়িতে এসেও গল্প বলে। এসময়ে তাদের গল্প বলার চেষ্ঠাকে উৎসাহিত করা গুরক্ষপূর্ণ। আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে গল্প বলার জন্য শিশুকে কখনো জোর করা যাবে না। সে যা কিছুই করুক না কেন সেটা স্বতস্ফুর্তভাবে করতে দিতে হবে। শিশুরা যখন গল্প বলবে তখন শিক প্রশ্ন করে তাদেরকে উৎসাহিত করতে পারেন। যেমন জিঙ্গাসা করতে পারেন , এরপর কি হলো? কিংবা তারপর তারা কি করলো? গল্প মোতাবেক প্রশ্ন করে গল্পটি শেষ করতে সহায়তা করতে হবে।
গল্প যে সবসময় কাশে একাকী বলা হয় তা নয়। দলগতভাবেও গল্প বলা যেতে পারে। দলগতভাবে গল্প বলার কয়েকটি কৌশল-
ক. একজনে একটি বাক্য। শিশুরা গোল হয়ে বসবে। এরপর প্রথম শিশুটি গল্পের এক লাইন বলবে। তারপাশের শিশুটি প্রথমবলা লাইনটির সাথে মিলিয়ে গল্পের দ্বিতীয় লাইনটি বলবে। এভাবে গল্প এগোতে থাকবে। শেষ শিশুটির বলার মধ্য দিয়ে যদি গল্প শেষ না হয় তবে প্রথমজন আবারো বলবে। এভাবে গল্পটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলবে। এই পক্রিয়ায় জানা গল্প যেমন বলা যায় তেমনি শিশুরা নতুন গল্পও তৈরী করতে পারে।
খ. বিষয়ভিত্তিক গল্পঃ এই ধরনের গল্পের জন্য প্রথমত সকলে মিলে একটি থিম বা বিষয়কে বেছে নেয়া হয়। যেমন একটি বিষয় হতে পারে দোয়েল পাখি। কিংবা শাপলা ফুল। কিংবা এক দেশে ছিল এক রাজা। ইত্যাদি।
গ. ছবি দেখে গল্প বলা ঃ এ ক্ষেত্রে বই থেকে কিংবা কোনো ছবি দেখে শিশুরা গল্প তৈরী করবে। এ ক্ষেত্রে তারা কল্পনার মাধ্যমে ছবিটি নিয়ে গল্প বানাবে।
ঘ.গল্পের ঝুড়িঃ এক্ষেত্রে একটি ঝুড়িতে অনেক জিনিস রাখা হয়। শিশূরা চোখ বন্ধ করে একটি করে জিনিস ঝুড়ি থেকে তোলে। এরপর যে জিনিসটি সে ঝুড়ি থেকে তুলল তার ভিত্তিতে একটি গল্প বলবে।
সাধারণত শিশূ প্রথমে শিক্ষকদের বলা গল্পটি তার মতো হুবহু বলার চেষ্ঠা করে। একসময় দেখা যায় শিশু গল্পের কাঠামো ঠিক রেখে নিজের মতো করে শব্দ ও বাক্য বলছে। এভাবে বলতে বলতে তার মধ্যে যখন আরো বেশী আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়। তখন সে নিজ থেকেই গল্প বানাতে শুরু করে। এ সময়ে সে তার পরিচিত জগতের বিষয় নিয়ে ছোট ছোট র্গপ বলে। সে সব গল্পে তার জানা শব্তগুলো ব্যবহার করে। এভাবে তার কল্পনার জগত যত প্রসারিত হয় ততোই সে নতুন নতুন র্গপ তৈরী করে। একপর্যায়ে তারা গল্প শুধু মুখে বলা নয় লিখতেও শুরু করে। এভাবে তারা নিজের তৈরী গল্প অন্যকে শোনায় এবং লিখিত ফরম্যাটে গল্পগুলো পরবর্তীতে বারবার নিজেরা পড়ে। এসময় তার মনে সৃষ্টি করার আনন্দ তৈরী হয়। শিশুরা গল্প লিখেই থেমে যায় না অনেক সময় তারা গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে ছবি আঁকে।
একজন উৎসাহী শিক্ষক যখন শিশূদের গল্প শোনায় তখন সে নিজেদের অর জ্ঞান ও ভাষা শেখাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।গল্প বলা ও গল্প শোনার মধ্য দিয়ে শিশু নিজেই গল্প বানাতে শুরু করে। একসময় শিশু গল্পের কাঠামো পরিবর্তন করতে শিখে। ভাষা ও শব্দ নিয়ে সে তখন নিজের অজান্তেই নানা ধরনের পরীা নিরিা করে। এভাবে শিশু ভাষা শেখে। তবে কে কতটা শিখবে সেটি নির্দিষ্ট শিশুর বয়স ও মেধার উপর নির্ভর করে। তবে এই পক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক শিশুই কিছু না কিছু শিখতে পারে।
Tuesday, 6 July 2021
শুভ জন্মদিন। নরেন্দ্র দেব। ০৭.০৭.২০২১. Vol - 426. The blogger in literature e-magazine
নরেন্দ্র দেব
জন্ম কলকাতার ঠনঠনিয়ার তৎকালীন বনেদি ও প্রগতিশীল পরিবারে। পিতা নগেন্দ্রনাথ দেব। জ্যাঠামহাশয় উপেন্দ্র চন্দ্র ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য। যৌবনে জ্ঞাতি-দাদা রাজেন দেবের প্রভাবে গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিলেও সাহিত্য-ক্ষেত্রেই জীবন কাটিয়েছেন। কলকাতার মেট্রোপলিটন স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন, কিন্তু স্বাস্থ্যের কারণে কলেজি শিক্ষা লাভ হয়নি। তবে সারাজীবন পড়াশোনার মধ্যেই নিয়োজিত থাকেন।
ব্রহ্মবান্ধবের সান্ধ্য পত্রিকাতে তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ "বসুধারা" , গল্পগ্রন্থ "চতুর্বেদাশ্রম" ও প্রথম উপন্যাস " গরমিল"। তবে 'ওমর খৈয়াম' -এর কাব্যানুবাদ ১৯২৬ সালে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং শিশু সাহিত্য — সর্বক্ষেত্রেই তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'ভারতী', 'কল্লোল', ' কৃত্তিবাস' ― বাংলা সাহিত্যের তিন যুগের এই পত্রিকাগুলির লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সমান হৃদ্যতা ছিল। তিনি বিখ্যাত নাট্য-সাপ্তাহিক 'নাচঘরের' ও 'প্রথম চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'বায়োস্কোপ'-এর পরিচালক ছিলেন। ছোটদের জন্য প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'পাঠশালা ' তিনি দীর্ঘ পনের বৎসর সম্পাদনা করেন। সাহিত্য জীবনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অক্ষয় বড়াল, কান্তকবি, নজরুল, মোহিতলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অন্তরঙ্গ ছিলেন। আবার সিনেমা-থিয়েটারের তৎকালীন শিল্পীরাও তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বালবিধবা সাহিত্যিক রাধারাণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সেকালের এক আলোচ্য বিষয় ছিল। এই বিবাহে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠান এবং শরৎচন্দ্র উপস্থিত থাকেন। নরেন্দ্র দেবের রচিত প্রথম ছোটদের নাটক 'ফুলের আয়না 'নাট্যাচার্য শিশিরকুমার' স্টার মঞ্চে প্রযোজনা করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ--
- ভ্রমণকাহিনী-
- রাজপুতের দেশে
- সাহেব-বিবির দেশে
- উপন্যাস-
- আকাশ কুসুম
- মানুষের মন
- কিশোর সাহিত্য-
- অনেক দিনের কথা
- আনন্দ মেলা
তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে 'ওমর খৈয়াম' এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'মেঘদূত' অনুবাদ করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স-সহ পশ্চিম ইউরোপ এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া, ফিনল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া ভ্রমণ করেন।
নরেন্দ্র দেব ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে "মৌচাক পুরস্কার ", 'ভুবনমোহিনী স্বর্ণ পদক' এবং ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে 'শিশিরকুমার পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দুবার সহ- সভাপতি, বেঙ্গল পি.ই.এন., শিশু সাহিত্য পরিষদ, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতির সভাপতি ছিলেন। ক্যালকাটা কেমিক্যাল ও রবীন্দ্রভারতী সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।
নরেন্দ্র দেব ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ শে এপ্রিল ৮২ বৎসর বয়সে কলকাতায় পরলোক গমন করেন।
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য। নগেন্দ্রনাথ বসু। ০৬.০৭.২০২১. Vol -425 . The blogger in literature e-magazine
রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা বিশ্বকোষের প্রথম পর্ব সম্পাদিত করেন। তবে পরবর্তী ২২টি পর্ব নগেন্দ্রনাথ বসু নিজে প্রকাশিত করেন, যা ১৯১১ সাল পর্যন্ত ২৭ বছর সময় নেয়। ২৪ পর্ব বাংলা বিশ্বকোষ ১৯১৬ এবং ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়।
তিনি তাঁর প্রথম কর্মজীবনে কবিতা ও উপন্যাস লেখালেখি শুরু করেন. অল্পদিন পরেই তিনি সম্পাদনা কাজে মনোনিবেশ করেন। এ সময় তিনি তপস্বিনী ও ভারত নামে দুটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি কায়স্থসভার কায়স্থ পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। শুধু পত্রিকাই নয়, তিনি অনেক মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থও সম্পাদনা করেন, যেমন: পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, চন্ডীদাসের অপ্রকাশিত রচনাবলি, জয়নারায়ণের কাশী-পরিক্রমা, ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী প্রভৃতি। এগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত হয়।
তিনি একজন বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ সংগ্রহের জন্য তিনি ভারতের নানা স্থান, বিশেষত, উড়িষ্যার বিভিন্ন তীর্থ ও দুর্গম স্থান ঘুরে বেড়ান। সেসব স্থান থেকে তিনি প্রচুর শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন বাংলা, সংস্কৃত ও উড়িয়া পুথি সংগ্রহ করেন। প্রাপ্ত লিপিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো শুশুনিয়া প্রত্নলিপি, মদনপালের অনুশাসন ইত্যাদি। এগুলির পাঠোদ্ধার করে তিনি প্রকাশ করেন যা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া নিজের সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সংশ্লিষ্ট স্থানের প্রাচীন ইতিহাস এবং নাগরাক্ষরের উৎপত্তি সস্পর্কে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে প্রাচীন পুথিগুলি সংগ্রহ করেন, সেগুলি নিয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ খোলা হয়।
তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা করার জন্য ব্যাপক ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও উড়িয়াতে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং পাথর ও তামার প্লেটের উপর অঙ্কন করেছেন।
১৮৮৪ সালে নগেন্দ্রনাথ শব্দেন্দু মহাকোষ নামে একটি ইংরেজি-বাংলা অভিধান সংকলন ও প্রকাশ করেন। এ কাজের সূত্র ধরেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় আনন্দকৃষ্ণ বসু ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সঙ্গে এবং তাঁদের আগ্রহেই তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন। ১৮৯৪ সালে বাংলার অনেক ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলি তিনি এখানে উপস্থাপন করেন। নগেন্দ্রনাথ শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট সংকলনের কাজেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাগ্রন্থ হলো: বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (কয়েক খন্ড), কায়স্থের বর্ণপরিচয়, শূন্যপুরাণ, Archaeological Survey of Mayurbhanja, Modern Buddhism and its Followers in Orissa, Social History of Kamrup ইত্যাদি।
গবেষণার পাশাপাশি নগেন্দ্রনাথ নাটক রচনা ও অনুবাদের কাজও করেন। বিহারীলাল সরকারের আগ্রহে তিনি দর্জিপাড়া থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবের জন্য শঙ্করাচার্য (১৮৮৮), পার্শ্বনাথ, হরিরাজ, লাউসেন প্রভৃতি গদ্যপদ্যময় কয়েকটি নাটক রচনা করেন। এছাড়া তিনি শেক্সপীয়রের হ্যামলেট এবং কর্ণবীর (১৮৮৪) নামে ম্যাকবেথ নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। নগেন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ। এছাড়া তিনি কায়স্থসভারও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।
তিনি "প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব" শিরোনামে ভূষিত হন। নগেন্দ্রনাথ বসুর কাজকে সম্মান জানিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা "বিশ্বকোষ" লেন নামে একটি রাস্তার নামকরণ করেছে।
মৃত্যু - ১১ ই অক্টোবর ১৯৩৮ সালে কাটাপুকুর বাসভবনে।
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
Monday, 5 July 2021
জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য। কাদম্বরী দেবী । ০৫.০৭.২০২১. Vol -424. The blogger in literature e-magazine
"চেয়ে তব মুখপানে বসে এই ঠাঁই
প্রতিদিন যত গান তোমারে শুনাই
বুঝিতে কি পার সখি, কেন যে তা গাই?
বুঝ না কি হৃদয়ের
কোন খানে শেল ফুটে
তব প্রতি কথাগুলি
আর্তনাদ করে উঠে!”
(সন্ধ্যাসঙ্গীত- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
" চতুর্দোলায় চড়ে একটি ছোট্ট মেয়ে 'গোধূলি লগ্নের সিঁদুরি রঙে'-রাঙা চেলি পরে প্রবেশ করলেন ঠাকুরবাড়িতে। তাঁর কাঁচা শ্যামলা হাতে সরু সোনার চুড়ি, 'গলায় মোতির মালা সোনার চরণচক্র পায়ে।'
কাদম্বরী দেবীজুলাই ৫, ১৮৫৯ সালে কলকাতায় কাদম্বরীর জন্ম। পৈতৃক নাম মাতঙ্গিনী। তিনি ছিলেন ঠাকুরবাড়ির বাজার সরকার শ্যাম গাঙ্গুলির তৃতীয় কন্যা। মাত্র নয় বছর বয়সে ১৯ বছর বয়সী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে কাদম্বরীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার শিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তার পিতামহ জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন একজন গুণী সংগীত শিল্পী। তার থেকেই কাদম্বরী এবং রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে গান শিখেছিলেন।ধীরে ধীরে ছোট্ট কাদম্বরীই হয়ে উঠলেন ঠাকুরবাড়ির যোগ্যতমা বৌমা। তিন তলার ছাদের ওপর গড়ে তুললেন 'নন্দন কানন'। পিল্পের ওপর সারি দিয়ে বসানো হল লম্বা পামগাছ, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, করবী, দোলনচাঁপা। এল নানারকম পাখি। দেখতে দেখতে বাড়ির চেহাড়াই বদলে গেল।
সমবয়সী হওয়ার সুবাদে কাদম্বরীর সাথে রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গল্প, কবিতা, নাটক আর গান রচনায় উৎসাহ যুগিয়েছেন তার সৃষ্টিশীল মতামত প্রদানের মাধ্যমে।কাদম্বরী অসাধারণ সাহিত্যপ্রেমী ছিলেন। তিনি শুধু সময় কাটানোর জন্যই বই পড়তেন না, উপভোগও করতেন। দুপুরবেলা রবি ঠাকুর তাঁকে নিজের লেখা পড়ে শোনাতেন। হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতেন বৌঠান। 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে তাঁর নাম ছিল না ঠিকই, কিন্তু তিনিই ছিলেন এই কবিতার প্রাণ . সেটা প্রকোট হয় তাঁর মৃত্যুর পর।
নন্দন কানন'-এ সন্ধেবেলায় বসত গান ও সাহিত্যপাঠের পরিপাটি আসর। মাদুরের ওপর তাকিয়া, রূপোর রেকাবে ভিজে রুমালের ওপর বেলফুলের গোড়ের মালা, এক গ্লাস বরফজল, বাটা ভর্তি ছাঁচি পান সাজানো থাকত। কাদম্বরী গা ধুয়ে, চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন সেখানে। জ্যোতিরিন্দ্র বাজাতেন বেহালা, রবীন্দ্র ধরতেন চড়া সুরের গান। বাড়ির অনেকে যোগ দিতেন সে আসরে। বাইরে থেকে আসতেন অক্ষয় চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী শরৎকুমারী, জানকীনাথ, মাঝে মাঝে আসতেন কবি বিহারীলাল।
রবীন্দ্রনাথ এবং কাদম্বরী ছিলেন খুবই ভালো বন্ধু এবং সহপাঠী যার কারণে এই দুজনের সম্পর্ক নিয়ে সেই সময়ে সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন বিতর্ক এখনো বিদ্যমান রয়েছে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহের (১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর) চার মাস পরে ১৯ এপ্রিল, ১৮৮৪ সালে কাদম্বরী দেবী আফিম খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, এবং তার দুই দিন পর এপ্রিল ২১ তারিখে মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান।জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার এই আত্মহত্যার বিষয়ে নিরব ছিল।
মুলত পারিবারিক সমস্যার কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে বিতর্ক রয়েছে। হিন্দু প্রথা অনুযায়ী তাকে মর্গে পাঠানো হয় নি, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেই বসানো হয়েছিল করোনার কোর্ট। গবেষকরা মনে করেন, স্বয়ং মহর্ষির উদ্যোগেই রিপোর্ট লোপ করা হয়, সঙ্গে লোপাট করা হয় 'সুইসাইড নোট'। ৫২ টাকা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয় সংবাদ মাধ্যমের। তাই কাদম্বরীর মৃত্যু সংবাদ তখন কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি।
কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং তার স্মৃতি নিয়ে মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও একাধিক কবিতা, গান ও গল্প রচনা করেছেন।
কবির ভাষায় -
"বড় ভালবাসতুম তাঁকে। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতেন। এই ভালবাসায় নতুন বৌঠান বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে আমার প্রাণের তার বেঁধে দিয়ে গেছেন। তাই তো সারাজীবন চলে তাঁর অনুসন্ধান: ''নয়ন সম্মুখে তুমি নাই/ নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।''
বাঙালি নাট্যকার, সঙ্গীতস্রষ্টা, সম্পাদক এবং চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রবধু এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদি।
#কাদম্বরী দেবীর শেষ চিঠি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর জন্য)
ঠাকুরপো
আজকাল তোমার ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়। সেটাই তো স্বাভাবিক। মাত্র চারমাস বিয়ে হয়েছে তোমার’।‘আগে তো সূর্য ওঠার আগে তুমি উঠতে। আমার ঘুম ভাঙাতো তোমার সকালবেলার গান। আমরা একসঙ্গে যেতাম নন্দনকাননে। ...
তারপর একদিন সেই বাগানে ভোরের প্রথম আলোয় আমাকে চুমু খেয়ে জিগ্যেস করলে- ‘নতুন বউঠান, নামটা তোমার পছন্দ হয়েছে?’ আমার সমস্ত শরীরের তখন কাঁটা দিচ্ছে। আবার ভয়ে বুক করছে দুরদুর। ঠাকুরপো, ‘এমন দুঃসাহস ভালো নয়, কেউ দেখে ফেললে...’!
বৃষ্টিতে ভিজছ তুমি। ...তোমার আয়ত দুটি চোখে মেঘলা আকাশের মায়া। তুমি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলে, ‘ঠাকুরবাড়িতে একটি উপবাসে আমরা সবাই কষ্ট পেয়েছি। চিরকাল, আদরের উপবাস’। ...তোমার মুখের দিকে মুখ তুলে বললাম, ‘আমাকে একটু আদর করবে ঠাকুরপো? কতদিন – কতদিন কোনও আদর পাইনি আমি। তুমি যেন জলদেবতা। সামান্য নীচু হলে তুমি। আমার মুখখানি তুলে নিলে কত আদরে – চুমু খেলে আমার ঠোঁটে। এক ঝলকের আলতো চুমু। মনে হল, এই প্রথম আদর পেলাম আমি’।
‘যখন যাব চলে ওরা ফুটবে তোমার কোলে,/ তোমার মালা গাঁথার আঙুলগুলি মধুর বেদনভরে/ যেন আমায় স্মরণ করে...অলস দ্বিপ্রহরে’।
‘
মৃত্যু যতই এগিয়ে আসছে, বিদায়ের ঘণ্টা যতই শুনতে পাচ্ছি, ততই যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মন, ভাবনারা সব ছড়িয়ে যাচ্ছে।
‘ঠাকুরপো, কথায়-কথায় খেই হারিয়ে কোথায় চলে এলাম। তোমাকে তো বলেইছি, মনটা বড্ড এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারছি না’।
শুভ জন্মদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । একজন বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। Dt -26.11.2024. Vol -1059. Tuesday. The blogger post in literary e magazine.
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২৬ নভেম্বর ১৮৯০ — ২৯ মে ১৯৭৭) একজন বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ. মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্...
-
যোগীন্দ্রনাথ সরকার (২৮ অক্টোবর, ১৮৬৬ - ২৬ জুন, ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) বা (১২ কার্তিক, ১২৭৩ - ১২ আষাঢ়, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) একজন খ্যাতনামা ভারতীয় ...
-
সুখলতা রাও (২৩ অক্টোবর,১৮৮৬- ৯ জুলাই,১৯৬৯) একজন বাঙালি সাহিত্যিক ও সমাজসেবী যিনি ১৮৮৬ সালের ২৩ শে অক্টোবর, কলকাতায় বিখ্যাত শিশুসাহিত্যি...
-
রাজা অজিত সিং বাহাদুর (১৬ অক্টোবর ১৮৬১ - ১৮ জানুয়ারী ১৯০১) বিবেকানন্দ লিখেছেন— "আমি আপনার কাছে আরও একটি অনুরোধ করব— যদি সম্ভব হয় আমা...