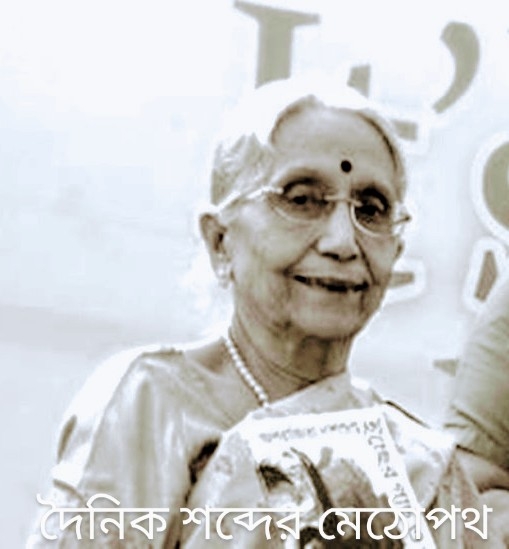Friday, 25 December 2020
দৈনিক শব্দের মেঠোপথ
Thursday, 24 December 2020
দৈনিক শব্দের মেঠোপথ। কবিতা
Wednesday, 23 December 2020
দৈনিক শব্দের মেঠোপথ
Tuesday, 22 December 2020
দৈনিক শব্দের মেঠোপথ
Monday, 21 December 2020
দৈনিক শব্দের মেঠোপথ
Sunday, 20 December 2020
দৈনিক শব্দের মেঠোপথ
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ্য
গোলাম মোস্তফা
==========∆∆∆∆∆==============
Doinik Sabder Methopath
Vol -227.dt -21.12.2020
৫ পৌষ,১৪২৭. সোমবার
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷∆∆∆∆∆÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
"লক্ষ আশা সন্তরে লক্ষ আশা অন্তরে
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে"
গোলাম মোস্তফার জন্ম ১৮৯৭ সালের ২১ শে ডিসেম্বর যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার শৈলকূপা থানার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে। পিতা কাজী গোলাম রব্বানী, পিতামহ কাজী গোলাম সরওয়ার। তারা ছিলেন সাহিত্যানুরাগী-ফারসী ও আরবী ভাষায় সুপন্ডিত। তার তিন পুত্রের মাঝে একজন হলেন বিখ্যাত পাপেটনির্মাতা ও চিত্রশিল্পী মুস্তফা মনোয়ার এবং সাম্প্রতিককালের অস্কারজয়ী বাংলাদেশী নাফিস বিন জাফর তার নাতিনী।গোলাম মোস্তফার শিক্ষা জীবনের সূচনা হয় চার বছর বয়সে নিজগৃহে ও পার্শ্ববর্তী দামুকদিয়া গ্রামের পাঠশালায়। কিছুদিন পরে তিনি ফাজিলপুর গ্রামের পাঠশালাতে ভর্তি হন। দু’বছর এই পাঠশালায় বিদ্যা অর্জনের পরে তিনি ভর্তি হলেন শৈলকূপা উচ্চ ইংরেজি স্কুলে। ১৯১৪ সালে এই স্কুল থেকে বিশেষ কৃতিত্বের সাথে তিনি প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি দৌলতপুর বি. এল কলেজ থেকে আই. এ এবং ১৯১৮ সালে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন। পরে ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ থেকে বি. টি ডিগ্রীও লাভ করেন।১৯২০ সালে জানুয়ারী মাসে ব্যারাকপুর সরকারি হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক হিসেবে গোলাম মোস্তফার শিক্ষকতা জীবনের সূচনা হয়। ১৯২৪ সালে ব্যারাকপুর হাই স্কুল থেকে তিনি কলকাতা হেয়ার স্কুলে বদলী হন। দীর্ঘদিন এখানে শিক্ষকতা করার পর তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় বদলী হন। সেখান থেকে ১৯৩৫ সালে বালিগঞ্জ সরকারি ডিমনেষ্ট্রেশন হাই স্কুলে বদলী হয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হন এবং কয়েক বছর পর উক্ত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদমর্যাদা লাভ করেন। এই বিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম মুসলিম প্রধান শিক্ষক। ১৯৪০ সালে তিনি বাঁকুড়া জিলা স্কুলে বদলী হন। শিক্ষকতা জীবনে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করার পর ১৯৪৬ সালে তিনি ফরিদপুর জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯৫০ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।
সাহিত্যকর্ম
রক্তরাগ (১৯২৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্য-কাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৯৩৬), হাস্নাহেনা (১৯৩৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯), তারানা-ই-পাকিস্তান (১৯৫৬), বনিআদম (১৯৫৮), গীতিসঞ্চালন (১৯৬৮) ইত্যাদি তাঁর মৌলিক কাব্য এবং মুসাদ্দাস-ই-হালী (১৯৪১), কালামে ইকবাল (১৯৫৭), শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া (১৯৬০) অনুবাদকাব্য। তিনি আল-কুরআনও (১৯৫৮) অনুবাদ করেন। তাঁর গদ্যরচনার মধ্যে বিশ্বনবী (১৯৪২), ইসলাম ও কমিউনিজম (১৯৪৬), ইসলাম ও জেহাদ (১৯৪৭), আমার চিন্তাধারা (১৯৫২), পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ইত্যাদি প্রধান। তাঁর বিশ্বনবী গ্রন্থখানি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এতে তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে ঐতিহাসিক মহামানব হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন।
গোলাম মোস্তফার কাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো সহজ ও শিল্পসম্মত প্রকাশভঙ্গি এবং ছন্দোলালিত্য। তিনি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেন এবং সেগুলি অবিভক্ত বাংলায় খুবই সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর কয়েকটি কবিতা স্কুলপর্যায়ে পাঠ্য ছিল।
তিনি গীতিকার ও গায়ক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর গানের বিষয় ছিল ইসলামি সংস্কৃতি ও দেশপ্রেম। পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিকায় বহু ইসলামি ও দেশাত্মবোধক গান তিনি রচনা করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর নিজের সুরারোপিত কয়েকটি গানের রেকর্ডও পাওয়া যায়। তার মধ্যে আববাসউদ্দীনের সঙ্গে গাওয়া রেকর্ডও রয়েছে। ব্যক্তিজীবনে গোলাম মোস্তফা ছিলেন খুবই সহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ। সাহিত্য-সংস্কৃতিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি যশোর সংঘ কর্তৃক ‘কাব্য সুধাকর’ (১৯৫২) এবং পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ‘সিতারা-ই-ইমতিয়াজ’ (১৯৬০) উপাধি লাভ করেন। [শহিদুল ইসলাম]
মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত কবি গোলাম মোস্তফার অবদান বাংলা সাহিত্যে এক বিরল দৃষ্টান্ত। স্কুল জীবনেই এই কবির সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এ সময় তাঁর ‘আর্দ্রিয়ানোপল উদ্ধার’ কবিতাটি মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার প্রথম কাব্য গ্রন্থ ‘রক্ত রাগ’ প্রকাশিত হলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিচের দু’লাইন কবিতার মাধ্যমে কবিতার মাধ্যমে কবিকে অভিনন্দিত করেছিলেন-
“তব নব প্রভাতের রক্তরাগখানি মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।”
তাঁর পরবর্তী গ্রন্থাবলীর মধ্যে ‘হাসনাহেনা’ (কাব্যগ্রন্থ) ‘খোশরোজ’ (কাব্যগ্রন্থ), ’সাহারা (কাব্যগ্রন্থ)’, ‘বুলবুলিস্তান’ (কাব্যচয়ন) ও ‘রূপের নেশা’ ‘ভাঙ্গাবুক’ ‘একমন একপ্রাণ’ ইত্যাদি উপন্যাসগুলি বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।
অনুবাদক হিসেবেও কবি গোলাম মোস্তফার বিশেষ খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায়। আরবী ও উর্দু সাহিত্য হতে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ভাষান্তরিত করে বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। ‘ইখওয়ানুস সাফা’, ‘মুসাদ্দাস-ই-হালী’,- ‘কালাম-ই-ইকবাল’, ‘শিকওয়া’ ও ‘আল-কুরআন’ তার ভাষান্তরিত গ্রন্থগুলির অন্যতম। এছাড়া, চিন্তামূলক ও যুক্তিবাদের উপর লিখিত আরও কিছু গ্রন্থাবলী তিনি রচনা করেছিলেন। ‘ইসলাম ও কমিউনিজম’, ‘ইসলামে জেহাদ’, ‘আমার চিন্তাধারা’, এগুলি তার গভীর চিন্তাধারার জ্ঞানলব্ধতার ফসল।
কবি গোলাম মোস্তফার ‘বিশ্বনবী’ একটি আশ্চর্য রকমের সফল সৃষ্টি। এই অমর গ্রন্থখানি গদ্যে রচিত হলেও সে গদ্যও কবিতার মত ছন্দময় এবং মধুর। গ্রন্থখানা বিশ্বনবী হয়রত মুহম্মদ এর একটি সার্থক জীবন চরিত]। গ্রন্থটিতে হৃদয়ের আবেগ, আন্তরিক অনুভূতি যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তার তুলনা আমাদের বাংলা সাহিত্যে নিতান্তই বিরল। এর পরবর্তীকালে তিনি কোর-অনিক ঘটনার অমিত্রাক্ষর ছন্দে ‘বনি আদম’ নামে একটি মহাকাব্য লিখেছিলেন। যা বাংলা সাহিত্যে এক অমর ও অক্ষয় কীর্তি।
সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গায়ক ও গীতিকার হিসেবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশেষ করে ইসলামী গান, গজল ও মিলাদ মাহফিলের বিখ্যাত ‘কিয়ামবাণী’ (রসুল আহবান বাণী) রচনায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তার অনেকগুলি গান আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠেও রেকর্ড হয়েছিল। এছাড়া নিজের কণ্ঠেও তিনি বেশ কয়েকটি গান রেকর্ড করেছিলেন। তার রেকর্ডকৃত গানগুলোর প্রথম লাইনগুলি নিম্নরূপ :
হে খোদা দয়াময় রাহমানুর রাহিম
বাদশা তুমি দীন ও দুনিয়ার নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি
আমার মুহম্মদ রাসুল
মৃত্যু :
বাংলা সাহিত্যের সাধক কবি গোলাম মোস্তফা তার শেষ জীবনের কয়েক বছর ঢাকা শান্তিনগরস্থ নিজ গৃহে (মোস্তফা মঞ্জিল) অতিবাহিত করেন। বেশ কিছু দিন রোগ যন্ত্রণা ভোগ করার পর কবি ১৯৬৪ সালের ১৩ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
Saturday, 19 December 2020
দৈনিক শব্দের মেঠোপথ
শুভ জন্মদিন শ্রদ্ধাঞ্জলি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । একজন বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। Dt -26.11.2024. Vol -1059. Tuesday. The blogger post in literary e magazine.
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (২৬ নভেম্বর ১৮৯০ — ২৯ মে ১৯৭৭) একজন বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ. মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্...
-
যোগীন্দ্রনাথ সরকার (২৮ অক্টোবর, ১৮৬৬ - ২৬ জুন, ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) বা (১২ কার্তিক, ১২৭৩ - ১২ আষাঢ়, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) একজন খ্যাতনামা ভারতীয় ...
-
সুখলতা রাও (২৩ অক্টোবর,১৮৮৬- ৯ জুলাই,১৯৬৯) একজন বাঙালি সাহিত্যিক ও সমাজসেবী যিনি ১৮৮৬ সালের ২৩ শে অক্টোবর, কলকাতায় বিখ্যাত শিশুসাহিত্যি...
-
রাজা অজিত সিং বাহাদুর (১৬ অক্টোবর ১৮৬১ - ১৮ জানুয়ারী ১৯০১) বিবেকানন্দ লিখেছেন— "আমি আপনার কাছে আরও একটি অনুরোধ করব— যদি সম্ভব হয় আমা...