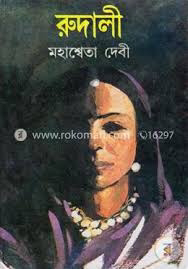স্যামুয়েল টেইলর কোলরিজ
মৃত্যু - ২৫ জুলাই ১৮৩৪ (বয়স ৬১)হাইগেট,
ইংল্যান্ড।
১৭৭২ সালের ২১ অক্টোবর ইংল্যাণ্ডের ডেভনশায়ারের অটারি সেন্ট মেরিতে স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের জন্ম হয়। তাঁর বাবা রেভারেণ্ড জন কোলরিজ ছিলেন কিংস স্কুলের এক সুপণ্ডিত স্কুলশিক্ষক এবং সেন্ট মেরি গির্জার এক যাজক। জন কোলরিজের দশম সন্তান কোলরিজ শৈশব থেকেই অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণ, অন্তর্মুখী, নির্জনতাপ্রিয় এবং সংবেদনশীল ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তিনি ‘আরব্য রজনী’, ‘বাইবেল’ পড়ে ফেলেছিলেন।
১৭৮১ সালে বাবার মৃত্যুর পরে লণ্ডনের ক্রাইস্ট হাসপাতালে কোলরিজের শিক্ষা শুরু হয়। পরে ১৭৯১ সালে তিনি ভর্তি হন কেমব্রিজের জেসাস কলেজে। এই সময় চিকিৎসাশাস্ত্র ও অধিবিদ্যায় তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মায়। হোমার এবং পিণ্ডারের রচনা তিনি অনায়াসে আবৃত্তি করতে পারতেন। প্রাবন্ধিক চার্লস ল্যাম্ব তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তিনি কোলরিজকে একজন ‘ইন্সপায়ারড চ্যারিটি বয়’ রূপে দেখতেন। কেমব্রিজে পড়াকালীন আরেক বন্ধু জন ইভান্সের বোন মেরির প্রেমে পড়েন কোলরিজ এবং এই প্রেমজনিত হতাশা আর রিপাবলিকান মতাদর্শের উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণে তাঁর প্রথাগত পড়াশোনায় ছেদ ঘটে। ১৭৯৪ সালের শেষ দিকে কোনো ডিগ্রি না নিয়েই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন।
কোলরিজের কর্মজীবন কখনোই সেভাবে স্থায়ী হয়নি। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে তিনি লণ্ডনে গিয়ে সৈনিকের পেশা গ্রহণ করেন। এর অনেক পরে ১৮০০ সালে লণ্ডনের ‘মর্নিং পোস্ট’ নামক সংবাদপত্রে রাজনৈতিক সংবাদলেখকের কাজে যোগ দেন তিনি। কিন্তু আর্থিক সচ্ছলতা তিনি কোনোদিনই উপভোগ করতে পারেননি। তবে তাঁর কর্মজীবনের এ ছিল পেশাগত অধ্যায়, আসলে তাঁর কর্মজীবনের পরিচিতি তাঁর লেখায়, সাহিত্যচর্চায়। ১৭৯৩ সালে তাঁর লেখা প্রথম দুটি কবিতা ‘অ্যাবসেন্স : অ্যান ওড’ ও ‘অ্যাবসেন্স : এ পোয়েম’ প্রকাশিত হয় ‘দ্য উইকলি এন্টারটেনার’-এ। ঠিক এর পরের বছর ১৭৯৪ সালে কোলরিজ লেখেন একটি নাটক ‘দ্য ফল অফ রোবস্পীয়র’ যা কোনোদিনই অভিনীত হয়নি। ১৭৯৬ সালে ব্রিস্টলের এক প্রকাশক জোসেফ্ কট্ল কোলরিজের কাব্যগ্রন্থ ‘পোয়েমস অন ভেরিয়াস সাবজেক্টস’ প্রকাশ করলে লণ্ডনে একজন উঠতি কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এর আগে ১৭৯৪ সালে ‘মর্নিং ক্রনিক্ল’-এ প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর লেখা ‘সনেটস অন এমিনেন্ট ক্যারেক্টারস’। প্রখ্যাত ইংরেজ রোমান্টিক কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। ১৭৯৮ সালে কোলরিজ এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগ্ম রচনা সংকলন ‘লিরিক্যাল ব্যালাডস’ প্রকাশ পায় যা ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের জন্ম দেয়। বলা হয় এই বইতে যে ভূমিকা লিখেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেটাই রোমান্টিকতার ধারণাকে বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। সারা ফ্রিকারের প্রেমে পড়ে তাঁকে নিয়ে কোলরিজ লিখে ফেলেন ‘দ্য ইউলিয়ান হার্প’ ও ‘টু দ্য নাইটিঙ্গেল’ নামে দুটি বিখ্যাত কবিতা। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও তাঁর বোন ডরোথির সান্নিধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রচনা তিনি এই সময়েই লিখে ফেলেন যা তাঁকে পরবর্তীকালে স্মরণীয় করেছে। ‘দ্য রাইম অফ দ্য অ্যান্সিয়েন্ট ম্যারিনার’, ‘ক্রিস্টাবেল (প্রথম অংশ)’ এবং ‘কুবলা খান’ তাঁর লেখা এসময়ের অন্যতম বিখ্যাত রচনা। ১৭৯৮ সালে নেদারস্টোয়িতে থাকার সময় কোলরিজ লেখেন ‘ফ্রস্ট অ্যাট মিডনাইট’ নামের একটি আত্মজীবনিমূলক কবিতা।
এরপরে স্থানবদল করে ১৮০০ সাল নাগাদ কোলরিজ কেস-উইকের গ্রেটা হলে থাকতে শুরু করেন যেখানে ক্রিস্টাবেলের দ্বিতীয় ভাগ লেখা শুরু হয় তাঁর। ইতিমধ্যে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। যন্ত্রণা উপশমের জন্য তিনি নিরন্তর আফিম সেবন করতে থাকেন। ফলে শারীরিক আর মানসিক দূর্বলতা তাঁকে ক্রমশ গ্রাস করে। এই পর্বে ১৮০২ সালে কোলরিজ লেখেন বিখ্যাত ‘ডিজেকশন : অ্যান ওড’ কবিতাটি। বন্ধু ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং আরো অনেকের পরামর্শে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটিতে তিনি বেশ কিছু বক্তৃতা দিয়েছিলেন সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ে। ১৮১৩ সালে ব্রিস্টলের ড্রুরি লেন থিয়েটারে ইংরেজ কবি বায়রনের সহযোগিতায় কোলরিজের লেখা ট্র্যাজেডি ‘রিমর্স’ প্রভূত সাফল্যের মুখ দেখেছিল। আর ১৮১৭ সালে যখন কোলরিজের কাব্যগ্রন্থ ‘সিবিলাইন লীভ্স’ এবং আত্মজীবনিমূলক গদ্যগ্রন্থ ‘বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া’ প্রকাশ পায় সমস্ত সমালোচক, কাব্যতাত্ত্বিকদের মুখে মুখে আলোচিত হতে থাকেন তিনি। এত কিছুর মধ্যে তাঁর দাম্পত্যজীবন ছিল অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত এবং যন্ত্রণাদায়ক। বারবার প্রেমে পড়েছেন কোলরিজ এবং প্রেম না পাবার যন্ত্রণা হতাশা তাঁকে গ্রাস করেছে। প্রথমে সারা ফ্রিকারকে বিবাহ করলেও দাম্পত্য সুখকর হয়নি, পরে ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্ত্রী মেরি হাচিনসনের বোন সারা হাচিনসনের প্রেমে পড়লেও বিবাহ করতে পারেননি কোলরিজ। পরবর্তীকালে চরম আর্থিক অনটনের সময়ে সারা হাচিনসনের আর্থিক সাহায্য কোলরিজকে যথেষ্ট অবলম্বন জুগিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বন্ধু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে নিয়ে ১৮০৭ সালে তিনি একটি প্রশস্তিমূলক কবিতা লেখেন ‘টু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ’ নামে।
১৮০৪ সাল থেকে ১৮০৭ সালের মধ্যে স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ ‘দ্য ফ্রেণ্ড’ নামে একটি রাজনীতি ও কবিতা-বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংরেজি সাহিত্য জগতে রোমান্টিক যুগের সূচনা করে কোলরিজ রোমান্টিকতার একটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত ‘বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া’ গ্রন্থে তিনি কল্পনা (Imagination) আর কাল্পনিকতা (Fancy)-র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। কোলরিজের মতে কাল্পনিকতা হল একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া যার কাজ হল ইন্দ্রিয়লব্ধ চিত্রকল্প (Image)কে একত্রিত করা আর কল্পনা হল একপ্রকার সঞ্জীবনী শক্তি যার কাজ বৈপরীত্যের মিলন।মুখ্য এবং গৌণ এই দুই প্রকার কল্পনার কথা বলেছেন কোলরিজ। ফলে খুব সহজ করে বলতে গেলে কোলরিজের তত্ত্বে কল্পনা হল বোধ, স্মৃতি, অনুষঙ্গ, অনুভূতি আর বুদ্ধির সংশ্লেষ। অতিপ্রাকৃতের রহস্য নিয়ে কোলরিজ যে কাব্যচর্চা করেছেন তার ফলে নিজের কাব্যচর্চায় ‘willing suspension of disbelief’-এর প্রয়োগ করেছিলেন তিনি। এর অনেক আগে কোলরিজ তাঁর ইংরেজ কবি বন্ধু রবার্ট সাদির সঙ্গে দার্শনিক গডউইনের নৈরাজ্যবাদী চিন্তার অনুকরণে একটি কমিউন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে বারোজন সুশিক্ষিত পুরুষ বাস করবে বারোজন নারীকে নিয়ে এক বৈষম্যহীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন জীবনে। সেই জন্যেই সাদি আর কোলরিজ বিবাহ করেন যথাক্রমে এডিথ ফ্রিকার ও সারা ফ্রিকারকে।
ফরাসি বিপ্লব ও বাস্তিল দূর্গের পতনকে কেন্দ্র করে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ কোলরিজ লিখেছিলেন ‘ওড টু দ্য ডিপার্টিং ইয়ার’ যা প্রকাশ পায় ১৭৯৬ সালে। আবার ফ্রান্স কর্তৃক সুইজারল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে মোহভঙ্গ ঘটে কোলরিজের, তিনি হতাশচিত্তে লেখেন ‘দ্য রিক্যান্টেশন : অ্যান ওড’ যা ১৭৯৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় ‘মর্নিং পোস্ট’ পত্রিকায়। এছাড়াও তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা হল ‘ফিয়ারস ইন সলিচিউড’। একদিকে অতিপ্রাকৃত রহস্যময়তা, প্রকৃতিকেন্দ্রিক ভাবুকতা অন্যদিকে তীব্র কল্পনাশক্তি, ইন্দ্রিয়ময়তা ছিল কোলরিজের কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু কবিতায় এবং বিহারীলাল চক্রবর্তীর ‘সঙ্গীত শতক’ কাব্যগ্রন্থে কোলরিজের কবিতার প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর রচিত অখ্যাত কিছু গদ্য ‘দ্য ওয়াচম্যান’, ‘অন দ্য কন্সটিটিউশন অফ দ্য চার্চ অ্যাণ্ড স্টেটস’, ৬ খণ্ডের ‘মার্জিনালিয়া’, ‘টেবল টক’ (১৯৯০), ২০০২ সালে প্রকাশিত ‘ওপাস ম্যাক্সিমাম’ ইত্যাদি সবই তাঁর মৃত্যুর পরে ক্যাথলিন কোবার্নের সম্পাদনায় দুই মলাটের মধ্যে সংকলিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
দাম্পত্যসঙ্গী -সারাহ ফ্রিকার।
সন্তান -সারা কোলরিজ, বারকেলি কোলরিজ, ডেরওয়েন্ট কোলরিজ, হার্টলে কোলরিজ।
একজন ইংরেজ কবি, সাহিত্য সমালোচক এবং দার্শনিক যে, তাঁর বন্ধু উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের সাথে ইংল্যান্ডের রোম্যান্টিক আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি লোক কবিদেরও (Lake Poets) সদস্য ছিলেন। কোলরিজ সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলো তার দ্য রাইম অফ দ্য অ্যান্সিয়েন্ট ম্যারিনার (The Rime of the Ancient Mariner) এবং কুবলা খান (Kubla Khan) কবিতার জন্য।বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া (Biographia Literaria) তাঁর সৃষ্ট একটি অন্যতম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ।
শেক্সপিয়ারের উপর তার সমালোচনামূলক কাজ ছিলো খুবই প্রভাবশালী, তাছাড়া তিনি ইংরেজি ভাষী সংস্কৃতিতে জার্মান ভাববাদী দর্শনের সূচনা করতে সাহায্য করেছিলেন।
তিনি রোমান্টিক হলেও তার Romanticism- এর মূল ভিত্তিই হলো ‘IMAGINATION,’-এ ক্ষেত্রে তার ‘DEJECTION- কবিতাটি থেকে কবিতাটির কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক-
DEJECTION
01. There was a time when, though my path was rough,
This joy within me dallied with distress,
And all misfortunes were but as the stuff
Whence Fancy made me dreams of happiness:
For hope grew round me, like the twining vine,
And fruits, and foliage, not my own, seemed mine.
But now afflictions bow me down to earth:
Nor care I that they rob me of my mirth;
But oh! each visitation
Suspends what nature gave me at my birth,
My shaping spirit of Imagination.
For not to think of what I needs must feel,
But to be still and patient, all I can;
And haply by abstruse research to steal
From my own nature all the natural man—
This was my sole resource, my only plan:
Till that which suits a part infects the whole,
And now is almost grown the habit of my soul.
Samuel Taylor Coleridge
Biographia Literaria,
Edited by J. Sawcross,
introduction, Page-xxxvi-xxxvii
In nothing does this loss of imaginative power exhibit itself more clearly than in the languor of his feelings in face of the beauties of nature. Even as he writes, he is gazing with indifference at the glories of the sun set’-Biographia Literaria vol-1
Introduction
02. And still I gaze—and with how blank an eye!
And those thin clouds above, in flakes and bars,
That give away their motion to the stars;
Those stars, that glide behind them or between,
Now sparkling, now bedimmed, but always seen:
Yon crescent Moon, as fixed as if it grew
In its own cloudless, starless lake of blue;
I see them all so excellently fair,
I see, not feel, how beautiful they are!
S. T. Coleridge
Biographia Literaria,
vol-1 Edited by J. Shawcross,
introduction, Page-xxxvi-xxxvii.
উদ্ধৃত কবিতাটির দুটি পংক্তি- যেখানে তিনি বলেছেন- ‘আমার চতুর্দিক থেকে জন্মিত প্রত্যাশালতা আমাকে বেষ্টিত করে। এবং যে প্রত্যাশার ফলমূল, পত্র পল্লব কিছুই আমার নয়, মনে হয় আমার মতো।’ -(ইংরেজী থেকে অনুবাদ- লেখক) । এর পরের আরো দুটি পঙক্তিতে তিনি আবার বলেছেন- ‘কিন্তু আমার শারীরিক দুর্বলতা, যন্ত্রণা আমাকে পৃথিবীর কাছে নত করে দিয়েছে। কিন্তু আমি ভ্রুক্ষেপ করি না যে তারা আমার আনন্দোচ্ছ্বাসকে হরণ করতে পারবে।’ -( ইংরেজী থেকে অনুবাদ- লেখক)।
কিন্তু আহ! প্রতিটি ঈশ্বর প্রদত্ত উপদ্রব
স্থগিত করে দেয়
আমার জন্ম লগ্নে প্রকৃতি আমাকে যা প্রদান করেছে
আমার কল্পনাবৃত্তির অনুপম অধিত্বকে। -(ইংরেজী থেকে অনুবাদ- লেখক)।
উদ্ধৃত কবিতাংশটুকুর মর্ম উদ্ধারে অতি তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টি এবং উপলব্ধি দিয়ে বোধ-গ্রাহ্য করতে চাইলে তীব্রভাবে প্রকট হয়ে ওঠে কোলরিজের এক প্রকারের অতিমাত্রিক বিষন্নতার প্রতিভাস। যদিও তিনি লিখেছেন তিনি অত্যন্ত স্বাতন্ত্র্যের সাথে সূর্যাস্তের অপার মহিমা স্থির দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। কিন্তু তার পরেও উল্লেখিত কবিতায় তিনি বিষন্নতাকে অস্বীকার করেন নি। যেখানে তিনি উন্মুক্ত বিশাল নীল আকাশের এক ফালি চাঁদের অবস্থানকে কল্পনা করেছেন- মেঘহীনতারকাবিহীন নীল সরোবরে স্থির এবং জন্মিত বলে। তার কাছে সব কিছুকেই মনে হয়েছে- সব কিছু চমৎকার, কত সুন্দর। নক্ষত্র বিহীন নির্মেঘ, নীলোক্ত মহাশুন্যের স্থির একটি চন্দ্রফালির অপরূপ সৌন্দর্যের মমতা তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে এবং এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই । কিন্তু এরই পাশাপাশি তিনি বলেছেন- ‘I see, not feel’-অর্থাৎ তিনি দেখেছেন মাত্র, মোটেই হৃদয়িক উষ্ণ অনুভব দিয়ে উপলব্ধি করেননি। তার দেখা এবং উপলব্ধি করণের মধ্যাঞ্চলবর্তী যে বিশাল এলাকা- সে এলাকাটিই বস্তুত আবৃত কোন কিছুর প্রতি তার অনাসক্ত বিষন্নতায়। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি যে কবিতাটি লেখেন এবং যার নামকরণ তিনি করেছেন ‘DEJECTION’’ -যার কিছু উদ্ধৃতি উপরের অংশে প্রদান করা হয়েছে। কবিতাটি লিখবার পর তিনি নিজের অভিজ্ঞতার প্রতি দুঃখবোধ করেছেন, বিলাপ করেছেন এবং তিনি ওই কবিতাটির মধ্যে এক প্রকারের আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন। যা তিনি চাননি। কিন্তু তাকেই তিনি তার অভিজ্ঞতার বিকাশ ঘটিয়ে উন্মোচিত করেছেন। আর এরই প্রেক্ষিতে-
He feels that he has lost his `shaping spirit of imagination, and that henceforth, he must be content with the prose of life, the investigation of the actual and the natural, considered strictly as such. For the spiritual in himself, if it be not dead, is yet lost to consciousness, and without it he lacks the key to the spiritual in nature.’ S.T.Coleridge, Biographia Literaria,vol-1 Edited by J. Shawcross, introduction, Page-xxxvi-xxxvii.
S. T. Coleridge- এর ‘Biographia Literaria’-গ্রন্থটির সম্পাদক J. Shawcross-এর উদ্ধৃত কথাগুলি তার মৌলিক সত্ত্বাকে আঘাত করেছে এভাবে। তিনি তার নিঃসীম কল্পনাগামীতা অথবা কল্পনাবৃত্তিকেও তার নিজ কল্পনায় স্থিত অধিত্বের উন্মেষগত অস্তিত্বকেও হারিয়ে ফেলেছেন। তাকে এখন এক প্রকার অতি সাধারণ বীক্ষণ সাধ্য নিরস, ছন্দহীন গদ্যময় জীবন, সে জীবনের প্রকৃতিগত সত্য অনুসন্ধান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।
তাঁর অভ্যন্তরে যে ধর্ম ভিত্তিক অধিত্ব্যবাদকে তিনি তারই রচিত কবিতার মাধ্যমে অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি এবং উদ্ধার করেছেন-যদি তার মৃত্যু না ঘটে তবে তার সচেতনতাকেও তিনি হারিয়ে ফেলবেন। যার মাধ্যমে তিনি প্রাকৃতিক অধিত্বের দ্বারোদঘাটন করবেন তার মূল চাবিটির অভাবেই ওই অধিত্বের দ্বারোদঘাটন আর তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না। এবং
To such a pass has he been brought by the deadening force of private affliction, health and the other materializing influences, all which, if not explicity referred to it in the personal lament are yet implied in the reflections with which it is entwined
এই কল্পনাবৃত্তির অধিত্ব যাকে Imagination- হিসেবে গ্রহণ করেছেন কোলরিজ এবং যার ওপর অবিচলভাবে বিশ্বস্ত থাকবার চেষ্টা করেছেন। সেই Imagination এর infinite influences, all which-ই যখন অগ্রাহ্য হয়ে যায় তার কবিতার নিগুঢ় অভ্যন্তরে তখন তাকেই তিনি উপলব্ধি করেন তার ব্যক্তিগত ‘consciousness’ এর অভাব হিসেবে । এবং তখনই তিনি আক্ষেপ করেন, ক্ষোভে ফেটে পড়তে চান। তার বিশ্বাসিত কবিতার সংজ্ঞা- ‘Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling-it takes it’s origin from emotion recollected in tranquility’- থেকে চ্যূত হয়ে যান। তখন তার মনে এক প্রকার উদ্বাহী ধারণা তাকে নিম্নগামীতার দিকে অনিরুদ্ধ ভাবে প্রলুদ্ধ করতে থাকে। আর সেখান থেকেই সৃষ্টি হয় তার- Dejection বা বিষন্নতা। আর এই বিষন্নতার ভয়াবহ সংক্রমণ থেকে কোনক্রমেই তিনি নিজেকে নিজের মৌলিক অবস্থানে পুনঃস্থাপিত করতে পারেন না। কোলরিজের অনেক দুর্বলতা, অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে এটাই বোধ করি সবচাইতে বেশি অধিগম্য দুর্বলতা। হয়তো নিজের কাছে নিজেরই এক প্রকার অভিশংস- যা তার সহ্যসীমার সীমায়তিকে লংঘন করে যায় বার বার।
কোলরিজ তাঁর প্রাপ্ত বয়স্ক জীবন ব্যাপী উদ্বেগ ও বিষণ্ণতার বিকলাঙ্গে ভুগেছিলেন; ধারণা করা হয় যে তিনি বাইপোলার ডিসর্ডারে ভুগেছিলেন যা তার জীবনকালে অসনাক্তই রয়ে গেছে। কোলরিজ দুর্বল স্বাস্থ্যে ভুগেছিলেন যার উৎপত্তি হয়েছিলো তার বাত জ্বর ও শৈশবকালীন অসুস্থতা থেকে। এই সব অসুস্থতার কারণে তাকে আফিমের আরক (laudanum) দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিলো যার ফলে সারা জীবন তার মধ্যে আফিমের আসক্তি প্রতিপালিত হয়।
তিনি অনেক পরিচিত শব্দ ও শব্দগুচ্ছ (words and phrases) উদ্ভাবন করেছিলেন যার মধ্যে প্রখ্যাত হচ্ছে suspension of disbelief । এমারসন এবং আমেরিকান অতীন্দ্রিয়বাদে তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিলো।
কুবলা খান কবিতাটির শুরু তিনি করেছেন এভাবে-
In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree:
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.
So twice five miles of fertile ground
With walls and towers were girdled round;
And there were gardens bright with sinuous rills,
Where blossomed many an incense-bearing tree;
And here were forests ancient as the hills,
Enfolding sunny spots of greenery.
But oh! that deep romantic chasm which slanted
Down the green hill athwart a cedarn cover!
A savage place! as holy and enchanted
As e’er beneath a waning moon was haunted
By woman wailing for her demon-lover!
And from this chasm, with ceaseless turmoil seething,
As if this earth in fast thick pants were breathing,
A mighty fountain momently was forced:
Amid whose swift half-intermitted burst
Huge fragments vaulted like rebounding hail,
Or chaffy grain beneath the thresher’s flail:
And mid these dancing rocks at once and ever
It flung up momently the sacred river.
Five miles meandering with a mazy motion
Through wood and dale the sacred river ran,
Then reached the caverns measureless to man,
And sank in tumult to a lifeless ocean;
And ’mid this tumult Kubla heard from far
Ancestral voices prophesying war!
The shadow of the dome of pleasure
Floated midway on the waves;
Where was heard the mingled measure
From the fountain and the caves.
It was a miracle of rare device,
A sunny pleasure-dome with caves of ice!
A damsel with a dulcimer
In a vision once I saw:
It was an Abyssinian maid
And on her dulcimer she played,
Singing of Mount Abora.
Could I revive within me
Her symphony and song,
To such a deep delight ’twould win me,
That with music loud and long,
I would build that dome in air,
That sunny dome! those caves of ice!
And all who heard should see them there,
And all should cry, Beware! Beware!
His flashing eyes, his floating hair!
Weave a circle round him thrice,
And close your eyes with holy dread
For he on honey-dew hath fed,
And drunk the milk of Paradise.
কবিতাটিতে অত্যন্ত প্রগাঢ়তা দিয়ে সুগভীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বোধের মাতৃকতা দিয়ে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করলে নিজের অন্তর্লোকাশ্রিত Imagination এর কোলরিজ সৃজিত কুবলা খানের স্বর্গসৌধের প্রতিবিম্বন চিত্তচৈতন্যে আপনা আপনি একটা অলৌকিক কল্পলোকের সৃষ্টি করে। সামান্যতম মুহুর্তের জন্য হলেও একটা তন্দ্রাচ্ছনতা একটা নিগুঢ় মোহময় পৃথিবীর আবেষ্টনীতে নিজেকে আবিষ্ট করে রাখে। কবিতাটি সরাসরি তাঁর পাঠককে মুহূর্তের মধ্যেই নিত্য সাধারণ বাস্তবতা থেকে, বাস্তবতা সংশ্লিষ্টতা থেকে একটি অতিঘোর স্বপ্নরাজ্যে স্থাপিত করে। কবিতাটি তাঁর আশ্চর্যতম শিহরণ জাত কল্পনাবৃত্তির অপরিমিত শক্তি দিয়ে দৃশ্যতঃ অথবা মোহগ্রস্ততার মধ্যে দিয়ে পাঠককে গোটা বিষয়টিকে প্রত্যক্ষ অধিগম্যতায় নিমজ্জিত করে। এসব ছাড়াও কবিতাটির মধ্যে আরও ভিন্ন মাত্রার কিছু গুনাবলীর মিশ্রণ যা একজন মানুষকে তার নির্দিষ্ট স্থান এবং কাল থেকে hypnotize করার মত করে অতিদূর লোকে অনায়াসেই নিয়ে যেতে পারে। যার মাত্রাগত দিকটি অবলীলায় সাধারণ সীমাবদ্ধতাকে অতি সহজেই অতিক্রম করতে পারে। সাধারণ প্রচলিত রীতি পদ্ধতির বাইরে একজন মানুষকে অলৌকিকত্বের প্রতি অত্য্শ্চার্য জাদুকরী কৃত্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুগত অথবা ভীতিযুক্ত করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে কবিতাটির কোন কিছুই চাক্ষুসমান হয় না। সবই থেকে যায় স্বপ্নলোকের নির্ধারিত নিরুদ্ধ সীমার গভীরে। আর এখানেই এস. টি কোলরিজের স্বর্গ হারানোর বহুমাত্রিক যন্ত্রণা, ব্যর্থতা আর বিষন্নতা। কবিতাটির কয়েকটি পঙক্তির মাধ্যমে কবি বিমোহিত হয়ে যান।
It was a miracle of rare device,
A sunny pleasure-dome with caves of ice!
A damsel with a dulcimer
In a vision once I saw:
It was an Abyssinian maid
And on her dulcimer she played,
Singing of Mount Abora.
Could I revive within me
Her symphony and song,
To such a deep delight ’twould win me,
That with music loud and long,
I would build that dome in air,
That sunny dome! those caves of ice!
And all who heard should see them there,
And all should cry, Beware! Beware!
His flashing eyes, his floating hair!
Weave a circle round him thrice,
And close your eyes with holy dread
For he on honey-dew hath fed,
And drunk the milk of Paradise.
একটি Dulcimer- নামীয় বিশেষ বাদ্য যন্ত্রের মাধ্যমে একটি আবিসিনীয় বালিকার কন্ঠে গীত মাউন্ট এ্যাবোরা নামক একটি সংগীতকে শ্রবণ করে মাত্র একটিবার তাকে দেখে। তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেন আমি কি তার বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর সুর এবং কন্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতকে আমার গভীর অন্তরে উজ্জীবিত করব। এই গভীর উৎফুল্লতা যা আমাকে জয় করে নিয়েছে তার উচ্চকিত এবং দূরগামী সঙ্গীতের মাধ্যমে। এই উৎফুল্লতা দিয়ে আমি শুনেও স্বর্গসম প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারি নির্মাণ করতে পারি সূর্যালোকিত স্বর্গীয় প্রাসাদ বরফাবৃত গুহা সমূহের মধ্যেও।
===={{{{{=={}{={{=}={{{={=}{{={=}={={{{{={==